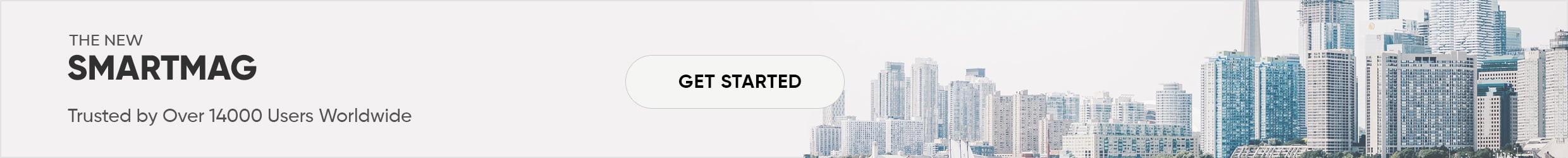দেশে গ্যাসের প্রকৃত মজুতের তথ্য এখনো অনাবিষ্কৃত। অনেক স্থানে অনুসন্ধান হয়নি। যেটুকু আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেখান থেকে মজুত ক্রমেই কমছে। ফলে জ্বালানি সমস্যা সমাধানে বাড়ছে এলএনজি-নির্ভরতা। নানা কারণে তরল গ্যাস আমাদানিতে জোর বাড়লেও দেশে নতুন কূপ, সন্ধান ও খননকাজে খুব বেশি গতি নেই। সাগরতলে গ্যাসের অফুরান সম্ভাবনার বিষয়টিও সেভাবে দেখা হচ্ছে না। এ অবস্থায় খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন নতুন অনুসন্ধান ও খননকাজ আরও ত্বরান্বিত হওয়া উচিত। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন লিমিটেড (বাপেক্স) এ বিষয়ে কাজ করলেও সেখানেও আছে কিছু সীমাবদ্ধতা। আবার গ্যাস আবিষ্কার ও উৎপাদন হলেও কিছু প্রান্তিক এলাকা থেকে কীভাবে তা মূল ভূখণ্ডে আনা হবে বা কীভাবে ব্যবহার হবে, এর জন্য নেই পর্যাপ্ত সঞ্চালনব্যবস্থা। সব মিলিয়ে এখনো ভবিষ্যতের জ্বালানি কীভাবে কম খরচে নিশ্চিত করা যাবে, সে বিষয়ে উদ্বেগ রয়েছে।
বিজ্ঞানী ও ভূতত্ত্ববিদদের মতে, বাংলাদেশে হাইড্রোকার্বন হাব হিসাবে গ্যাসের প্রধান মজুত সিলেট এবং এর আশপাশের এলাকায়। সেখানেও অনেক জায়গায় এখনো ব্যাপকতর অনুসন্ধান বাকি। ২০০৪ সালে নরওয়েজিয়ান বিজ্ঞানী প্রফেসর আর্লিং বাংলাদেশে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তিনি সে সময় হাতিয়া অঞ্চলে প্রায় ১২ টিসিএফ (ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট) প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত থাকার সম্ভাবনার কথা কয়েকজন ভূতাত্ত্বিককে জানান। পরবর্তী সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও ডেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেখানে প্রায় ৬.৫ টিসিএফ গ্যাস মজুত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়। ভোলা, শাহবাজপুর, সুন্দলপুর, ফেনী ও আশপাশের অঞ্চল এতে অন্তর্ভুক্ত। ইতোমধ্যে সেখানে প্রায় ১.৫ টিসিএফ গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও প্রায় ৫০০ বিসিএফ যুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, অতিরিক্ত খনন করলে ৩-৪ টিসিএফ গ্যাস পাওয়া অসম্ভব নয়।
বাপেক্সের তথ্য অনুযায়ী, ভোলায় গ্যাসের উল্লেখযোগ্য মজুত নিশ্চিত হয়েছে। সেখানে এখন পর্যন্ত বাপেক্স ৯টি কূপ খনন করেছে। অচিরেই আরও কয়েকটি কূপ খনন করা হবে। এসব অনুসন্ধান সম্পন্ন হলে গ্যাসের সার্বিক মজুত সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে। এখন পর্যন্ত শাহবাজপুরে গ্যাস মজুত আছে ১২২৫ বিসিএফ। উত্তর ভোলায় আছে ৬২২ বিসিএফ। ইলিশাতে আছে ২০০ বিসিএফ গ্যাস। সব মিলিয়ে ২০৪৭ বিসিএফ গ্যাস। যার মধ্যে উত্তোলনযোগ্য মজুত ১৪৩৩ বিসিএফ গ্যাস।
পেট্রোবাংলার উদ্যোগে ৫০টি কূপ খননের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, যার বেশির ভাগ কাজই করছে বাপেক্স। এর মধ্যে আছে অনুসন্ধান কূপ, মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপ এবং ওয়ার্কওভার কূপ। ইতোমধ্যে ১৯টি কূপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এখনো কোথাও বড় পরিসরে গ্যাসের সন্ধান মেলেনি। বাকি ৩৫ কূপ খননের সময়সীমা ধরা হয়েছে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত।
আরেক পরিকল্পনায় ১০০ কূপ খননের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ এবং কারিগরি কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সেখানেও থাকবে অনুসন্ধান, মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও ওয়ার্কওভার কূপ। তবে এসব কাজ মূলত ৫০ কূপের কাজ শেষ হওয়ার পর শুরু হবে। এ প্রকল্প শেষ হতে সময় লাগবে ২০২৯ সাল পর্যন্ত।
এদিকে বাপেক্সের কূপ খননের কাজে কিছু সীমাবদ্ধতার বিষয়ে জানা গেছে। এর মধ্যে প্রকল্প অনুমোদনে সময় বেশি নেওয়া, ভূমি অধিগ্রহণে সময়ক্ষেপণ, যন্ত্রপাতিসহ নানা কাজে দরপত্র দেওয়া, মালামাল প্রাপ্তিতে অধিক সময়, এলসিবিষয়ক জটিলতা প্রভৃতি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও ভূতাত্ত্বিক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া মনে করেন, ভবিষ্যতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশে অনুসন্ধানের পাশাপাশি দ্রুত কূপ খনন বাড়ানো জরুরি। অনুসন্ধান ও জরিপের বিষয়ে তিনি যুগান্তরকে বলেন, এখন পর্যন্ত স্থলভাগে ৪৬-৪৭ হাজার লাইন-কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক এবং প্রায় ৬ হাজার বর্গকিলোমিটার ত্রিমাত্রিক সিসমিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। এসব জরিপের ওপর ভিত্তি করে যত কূপ খনন করা হয়েছে, তাতে সফলতার হার ৩:১। অর্থাৎ প্রতি তিনটি কূপে একটি থেকে গ্যাস মজুত পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিকভাবে এ অনুপাত ৮:১ কিংবা ১০:১ হলেও বাংলাদেশে সফলতার হার অনেক বেশি। মোট উৎপাদন কম, কারণ খননকৃত কূপের সংখ্যা সীমিত। ড. ভূঁইয়া বলেন, এতদিন সিলেট-ট্রাফ ও তৎসংলগ্ন মধ্যাঞ্চলীয় ফোরডিপকে বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম হাব হিসাবে ধরা হতো। কিন্তু বর্তমান সফলতার ভিত্তিতে হাতিয়া ট্রাফসংলগ্ন এলাকাকে নতুন পেট্রোলিয়াম হাব হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তাই তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে দৃষ্টি এদিকে ফেরাতে হবে।
তিনি জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য পাঁচটি দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেন, ১. বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্র তিতাস, বিবিয়ানা প্রভৃতি বড় ক্ষেত্রগুলোয় গভীর খনন করে নতুন মজুত নিশ্চিত করা; অনাবিষ্কৃত স্তরগুলো শনাক্ত করা; আংশিক অনুত্তোলিত অংশগুলো ড্রিলিং-এর আওতায় আনা। ২. ক্ষেত্রগুলোর মাঝামাঝি স্থান-যেসব এলাকায় পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান হয়নি, সেখানে খনন বাড়ানো। ৩. হিঞ্জ-জোন : মোবারকপুর, জামালপুরে গ্যাস প্রমাণিত হয়েছে; তাই পাবনা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বরাবর হিঞ্জ-জোনেও অনুসন্ধান বাড়াতে হবে। ৪. কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার : চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ২৮টি এলাকায় জটিল ভূগঠন রয়েছে। সেখানে পর্যাপ্ত অনুসন্ধান হয়নি। পাশের ত্রিপুরার সাফল্য এবং সেমুতাংয়ে গ্যাসপ্রাপ্তির নজির এ অঞ্চলে সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছে। ৫. অফশোর অনুসন্ধান : ভিন্টেজ ডেটা (৫২ হাজার লাইন-কিমি.) ও নতুন সিসমিক ডেটা (১২ হাজার লাইন-কিমি.) কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক কোম্পানিকে প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডারে যুক্ত করতে হবে। ২০২৪ সালের টেন্ডার রাজনৈতিক কারণে আশানুরূপ ফল দেয়নি; তাই রোডশো ও নতুন আহ্বান দরকার।
তার মতে, আগামী ৫ বছরে ৫০টি বা ১০-১৫ বছরে ১০০টি কূপ খনন করা গেলে প্রতিটি কূপে গড়ে ২০০-২৫০ কোটি টাকা খরচ হবে। ৫০টি কূপে মোট খরচ দাঁড়াবে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু একটি ক্ষেত্র থেকেও যদি অন্তত ৫০০ বিসিএফ গ্যাস পাওয়া যায়, তবে তার বাজারমূল্য হবে প্রায় ৫০-৫৫ হাজার কোটি টাকা।
চলমান অনুসন্ধান থেকে প্রায় ৩ টিসিএফ গ্যাস প্রমাণিত হয়েছে। আগামী ২৫-৩০টি কূপ থেকে আরও ২ টিসিএফ পাওয়া সম্ভব। অতিরিক্ত ৫০টি কূপ থেকে প্রায় ১৫ টিসিএফ মজুত যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সাকসেস রেশিও (৩:১) অনুযায়ী অন্তত ৫ টিসিএফ গ্যাস নিশ্চিতভাবে পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে অবশিষ্ট মজুতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ টিসিএফ।
ড. ভূঁইয়ার মতে, এই গ্যাস মজুত (প্রায় ২০ টিসিএফ) নিশ্চিত করা গেলে ২০৪৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর প্রায় ১ টিসিএফ গ্যাস দেশীয় উৎস থেকে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি কিছু আমদানির মাধ্যমে চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে। এ সময়ে নবায়নযোগ্য শক্তি ও বিকল্প জ্বালানি উৎস আরও প্রসারিত হবে। এতে দেশের জ্বালানি খাতের অনিশ্চয়তা দূর হবে।
অনুসন্ধান কূপ খননে প্রকৃত অর্থে লোকসান নেই। কূপে গ্যাস পাওয়া গেলে সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহ সম্ভব হয়। এতে তরল গ্যাস আমদানিনির্ভরতা কমে। আর গ্যাস না মিললেও ভূগর্ভস্থ মূল্যবান ডেটা পাওয়া যায়, যা ভবিষ্যতের অনুসন্ধানে কাজে লাগবে।