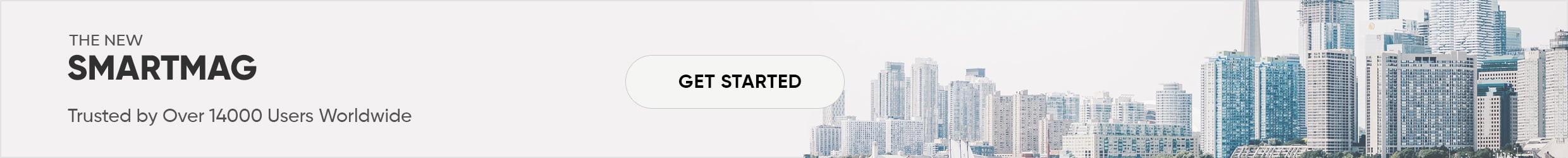‘জেন-জি’র আন্দোলন–অভ্যুত্থানে গত সপ্তাহে নেপালে এক উত্তাল অবস্থা দেখা গেল। শুধু জেন-জির কথা বললে ভুল হবে, নেপালের যুবারাও রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। প্রাথমিক উপলক্ষ ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা।
৮ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভে ১৯ জনের মৃত্যুর পর উত্তাল হয়ে ওঠে পুরো দেশ। পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি।
সরকার কিংবা বিরোধী দল, সব পক্ষের রাজনৈতিক দলের নেতাদের বাড়িতে হামলা হয়েছে। এমন একটি বাড়িতে দেওয়া আগুনে পুড়ে মারা গেছেন একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী। মন্ত্রীদের বিবস্ত্র করে রাস্তায় পেটানো হয়েছে।
সহিংসতার আগুনে যে কেবল রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িঘরই পুড়েছে, তা–ই নয়, পুড়ে গেছে সর্বোচ্চ আদালতের নথি, পার্লামেন্ট ভবন, প্রধানমন্ত্রীর অফিসসহ সরকারি অফিসের দলিল-দস্তাবেজ। এক বছর আগে চব্বিশের জুলাই–আগস্টে বাংলাদেশে সংঘটিত অনেক ঘটনার সঙ্গে এর মিল আছে সত্যি।
রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে না পারলে কেবল আদর্শের বুলি আওড়ালে মানুষের পেট ভরে না।
বাংলাদেশের এখনকার রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের উচিত নিজেদের ব্যর্থতার ভার অন্যের কাঁধে না চাপিয়ে নতুন করে আয়নায় মুখ দেখা।
কিন্তু বাংলাদেশে ৫ আগস্টের গণ–অভ্যুত্থানের পরপরই এর সম্মুখসারির নেতারা প্রত্যেকে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ফলে সরকার ও পুলিশের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, সেনাবাহিনীর একরকম নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও এ দেশের জেন-জিরা দ্রুতই নিজেদের সংবরণ করেছিলেন।
ছাত্র–তরুণেরা বরং রাস্তায় নেমে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন রাতারাতি—রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করেছেন, ময়লা–আবর্জনা পরিষ্কার করেছেন, মাদ্রাসার অনেক ছাত্র মন্দির পাহারা দিয়েছেন, এলাকার মানুষ একজোট হয়ে ডাকাত ঠেকিয়েছেন।
অভ্যুত্থানের অল্প কিছুদিন পর ভয়াবহ বন্যা ধেয়ে এলে পুরো দেশের মানুষ এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাই নেপালের সঙ্গে চব্বিশের বাংলাদেশের মিল-অমিল দুই–ই আছে।
চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানের আগে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ভরসা খুব একটা না থাকলেও দলগুলো গণ–অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিল। অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের পাশাপাশি তারাও নতুন সরকার গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। দিন শেষে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের ব্যাপারে দেশের মানুষকে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরই ভরসা রাখতে হয়। নানা ঘটনার পরিক্রমায় অভ্যুত্থানের অংশীদার হিসেবে দাবি করা ছাত্র–তরুণদের একটি অংশও নিজেদের রাজনৈতিক দল গঠন করে। এরপর তারা চলমান সংস্কারপ্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।
এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সংস্কারের কাজটিও প্রায় পুরোপুরি রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নির্ভরশীল। সেখানে অসংগঠিত সাধারণ জনগণের অংশ নেওয়ার সুযোগ সামান্যই।
নেপালের পরিচিত বা পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা অবশ্য বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেগতিক। ১৯৯৬ সাল থেকে চলা মাওবাদীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় ২০০৬ সালে। এরপর ২০০৮ সালে গণপরিষদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় মাওবাদীদের দল সিপিএন-এম। শুরু হয় নেপালের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা।
নেপালের সবচেয়ে পুরোনো দল নেপালি কংগ্রেস। দলটি ভারতপন্থী বলে পরিচিত ছিল। তা সত্ত্বেও দলটি রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে রূপান্তরের লড়াই–সংগ্রামে টিকে যায়। ২০১৫ সালে নতুন সংবিধান পায় নেপাল।
মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিল, ভেবেছিল এবার তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে।
সে আশা যে নিরাশার বালুচরে হারিয়ে গেছে, তার প্রমাণ নেপালে এবারের এ অভ্যুত্থান।
বামপন্থী হিসেবে পরিচিত দল সিপিএন-ইউএমএল নেতা কে পি শর্মা অলি কখনো জোট গড়েছেন মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দহল প্রচণ্ডের সঙ্গে, আবার বছর না ঘুরতেই সুযোগ বুঝে চোখ উল্টে চলে গেছেন ভারতপন্থী নেপালি কংগ্রেসের সঙ্গে।
এই নেতারা যেকোনো মূল্যে মসনদ আঁকড়ে থাকতে চেয়েছেন। তাই নতুন সংবিধান প্রণয়নের পর গত ১০ বছরে গড়ে প্রতি এক বছরে প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছে। এরই ফাঁকে দুর্নীতি ডালপালা মেলেছে সর্বত্র।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একদিকে রাজনীতিবিদদের সন্তানদের বিলাসী জীবন, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের নিরন্তর জীবনসংগ্রামের বৈপরীত্য দেখা গেছে। তাঁদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্যগুলো প্রকট হয়ে উঠেছিল।
এভাবে নেপালের মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে, তাদের নেতাদের কাছে ক্ষমতা আর অর্থবিত্তই সবকিছু; ডান কিংবা বাম আদর্শ তাঁদের মুখের বুলি মাত্র; বাস্তবে এগুলো ক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
একদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলাদেশে চব্বিশ সালে যা হয়েছে এবং এখন যা হচ্ছে, তা নেপালে হয়ে গেছে ১৭ বছর আগে।
এই ১৭ বছর ধরে নেপালের মানুষ স্বপ্ন দেখেছে; ভেবেছে, রাজতন্ত্রপন্থী রাজনীতিবিদের চেয়ে বামপন্থীরা হয়তো ভালো কিছু করে দেখাবেন। দিন শেষে তারা নিরাশ হয়েছে।
যারা নেপালের ঘটনাকে কেবল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করার প্রতিবাদ কিংবা বিদেশি ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখতে চায়, তারা বোধ হয় অনেক কিছু্ই দেখতে চেয়েও দেখছে না।
রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে না পারলে কেবল আদর্শের বুলি আওড়ালে মানুষের পেট ভরে না। তারা অপেক্ষা করে, আশায় বুক বাঁধে; কিন্তু একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, তখন কেউই রেহাই পায় না।
সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পর এটা ছিল দেশের প্রথম কোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্রার্থীরা বিরাট ব্যবধানে জয়ী হওয়ায় অনেকেই বিস্মিত, অনেকের মধ্যে প্রশ্ন দেখা গেছে।
এ মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপির কোনো কোনো নেতা এটাকে আওয়ামী লীগের ‘ষড়যন্ত্র’ কিংবা ‘ভোট কারচুপি’ আখ্যা দিতে মোটেই দেরি করেননি।
এ নির্বাচনের বড় অংশজুড়ে বিএনপি ও বামপন্থী সংগঠনের প্রার্থীরা শিবিরকে মোকাবিলা করতে চেয়েছেন ‘স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি’র মতো বয়ান দিয়ে। এটা ভুলে গেলে চলবে না, আওয়ামী লীগ ১৫ বছর ধরে এ বয়ান ব্যবহার করে জামায়াত-শিবিরেকে ঠেকানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।
এর বিপরীতে হিজাব পরেন না এমন নারী ও আদিবাসী চাকমা প্রার্থীকে নিজেদের প্যানেলে রেখেছিল ছাত্রশিবির। বিজয়ের পর ভিপি-জিএসসহ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রায়ের বাজারে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে একাত্তর ও চব্বিশের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।
বিজয়ের পর শিবিরের সাবেক নেতা মির্জা গালিব বিরোধীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্ম–পোশাকনির্বিশেষে নারীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। শিবিরের এ কাজগুলো তাদের এত দিনের কট্টর ডানপন্থী রাজনীতি থেকে কিছুটা হলেও সরে আসা।
কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও আছে। চট্টগ্রাম কিংবা রাজশাহীতে এবং সেখানকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, যেখানে দল হিসেবে জামায়াতের প্রভাব অনেক বেশি, তাদের ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবির আরও অনেক বেশি শক্তিশালী, সেখানে তাদের আচরণ এখনো পুরোনো ধাঁচেই রয়েছে গেছে। এসব ক্ষেত্রে পেশিশক্তির ব্যবহার, নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান ও কঠোরভাবে ভিন্নমত দমনের রাজনীতি থেকে তারা সরে এসেছে, এমনটা দৃশ্যমান নয়।
চব্বিশের জুলাইয়ের পর মুক্ত পরিবেশেও ছাত্রশিবির ‘গুপ্ত’ রাজনীতির ধারা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এসেছে, সেটা বলাও দুষ্কর। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তেও অনেকের শিবির পরিচয় সামনে এসেছে। জুলাইয়ের পরও এত দিন এ লুকোচুরির কী যৌক্তিকতা ছিল, সেটা নিশ্চয়ই একটা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়।
একই সঙ্গে সাইবার স্পেসে প্রতিনিয়ত মিথ্যা প্রচার, বিরোধীদের চরিত্রহননসহ নানা ধরনের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। অভ্যুত্থানের পরপর ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রামে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের কর্মীদের ওপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের নামে তথাকথিত সাধারণ ছাত্রদের দিয়ে হলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, এমনকি নিজেদের মতাদর্শের বিরোধী ছাত্রদের হলে উঠতে বাধা দেওয়ার অভিযোগও কম নয়।
ডাকসু বা অন্য কোনো ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের বিজয় কীভাবে হচ্ছে, তার চেয়ে ঢের বেশি বিশ্লেষণের দাবি রাখে বিএনপির ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল ও বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর পরাজয়ের কারণগুলো।
ছাত্রদল ও বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলো আদর্শিক বিতর্কে যতটা সময় ব্যয় করেছে, শিক্ষার্থীদের জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যা নিয়ে ততটা ভাবেনি। শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের সমস্যগুলো কী, কীভাবে সেগুলোর সমাধান হতে পারে—বেশির ভাগ ছাত্রসংগঠনের আলাপ–আলোচনা ও প্রচারণায় যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। তারা অনেকাংশে নির্ভর করেছে আদর্শিক বয়ানের ওপর।
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) ভরসা করতে চেয়েছে জুলাইয়ের চেতনার ওপর। নিঃসন্দেহে গণ–অভ্যুত্থানে বাগছাস মনোনীত ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের ও জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারের ভূমিকা ভুলে যাওয়ার মতো নয়। একইভাবে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী মো. আবিদুল ইসলাম ও জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম, স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা ও বামপন্থী মেঘমল্লার বসুর স্বৈরাচারবিরোধী দীর্ঘ লড়াই–সংগ্রামের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
কিন্তু গণ–অভ্যুত্থানের পরের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পূর্ববর্তী লড়াই–সংগ্রামের ইতিহাসের চেয়ে তাঁদের জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধানকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যবধানটা তৈরি হয়েছে সেখানেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন জাতীয় রাজনীতির প্রতিচ্ছবি না হলেও কিছুটা আভাস সেখান থেকে পাওয়া যায়, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। জুলাই অভ্যুত্থানের পর দেশের মানুষ জীবনযাপনে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল।
কেবল আদর্শের বুলিতে কিংবা রাজনৈতিক বয়ানে দেশের মানুষ চিরদিন সন্তুষ্ট থাকবে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের কাজ দিয়ে দেখাতে হবে, তারা পরিবর্তিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের জন্য তারা অতীতের চেয়ে ভিন্ন কিছু করে দেখাতে পারবে। সেখানেই অনেক কিছু শেখার আছে নেপালের বর্তমান অবস্থা আর ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল থেকে।
নেপালে যা ঘটেছে ২০০৮ সালে, বাংলাদেশে সেটা হয়েছে ২০২৪ সালে। মানুষ স্বপ্ন দেখেছে নতুন আশা নিয়ে বাঁচার, নতুনভাবে বাঁচার। ২০০৮ সালে নেপালে নতুন সংবিধান, নতুন রাজনৈতিক দল—সবই হয়েছিল; শুধু সাধারণ মানুষের জন্য নতুন একটা জীবনযাপনের আয়োজনের বিষয়টা কোন ফাঁকে যেন ভুলে গিয়েছিলেন রাজনীতিবিদেরা!
চব্বিশ–পরবর্তী বাংলাদেশেও সংবিধান, আইন, দল, রাজনীতি, ইহিতাস নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। এসব আলাপ অপ্রয়োজনীয় সেটা বলছি না। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যদি পরিবর্তন না আনা যায়, তবে নেপালের বর্তমান পরিস্থিতি বাংলাদেশে আসতে ১৭ বছর না–ও লাগতে পারে।
বাংলাদেশের এখনকার রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের উচিত নিজেদের ব্যর্থতার ভার অন্যের কাঁধে না চাপিয়ে নতুন করে আয়নায় মুখ দেখা। আশা ছিল, গত বর্ষাতেই কাজটা শুরু হবে, কিন্তু সেটা হয়নি। এ জন্য আর কত অপেক্ষা করতে হবে?