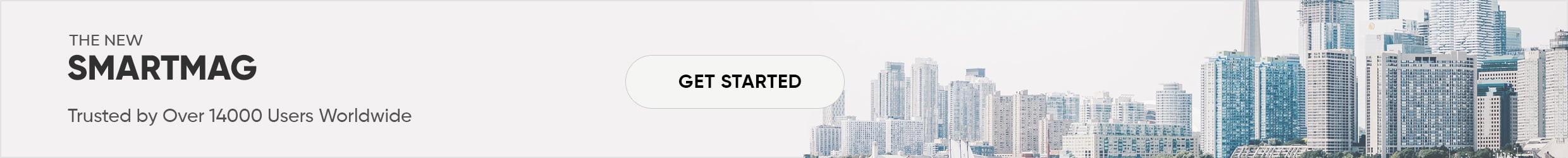বুয়েট শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি একটি আন্দোলন করছেন। ইতিমধ্যে সারা দেশের ডিগ্রি প্রকৌশলীদের এতে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তবে এ আন্দোলনের আগে বহুদিন ধরেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে ‘ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট’রা আন্দোলন করে আসছিলেন। প্রথমে সেই গল্প করা যাক।
আসলে এ অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে নানা ধরনের আন্দোলনের মাত্রা বহুগুণ বেড়েছে। আনসারদের পুলিশ বা সৈনিক হওয়ার আন্দোলন, ফেল করা এসএসসি/এইচএসসি ছাত্রদের অটো প্রমোশনের আবদার, আর এর সঙ্গে সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে ডিপ্লোমাদের গ্র্যাজুয়েট ‘প্রকৌশলী’ হওয়ার খায়েশ।
এ প্রসঙ্গে আজকাল ফেসবুকেও কিছু ভিডিও ভাইরাল হতে দেখা যাচ্ছে। এক ডিপ্লোমা ছাত্র একটা ছোট ড্রোন ওড়াচ্ছেন আর মুখে বলছেন, বুয়েট রিকশা বানায় আর তিনি রোবট বানান।
আরেক আন্দোলনকারী বলছেন, আইআইটি আর এমআইটি থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা নাকি তাঁদের মতো ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী। আবার গ্রামের জনৈক কারিগরের বিমান ওড়ানো দেখেও সবাই হতবাক!
বুয়েট কী করল? তথাকথিত জ্ঞানগর্ভ ‘মোটিভেশনাল স্পিকার’ও বিস্মিত! সাধারণ মানুষ না বুঝেশুনে এ অখাদ্যগুলো গিলছে আর মজা পাচ্ছে।
তারা জানে না, আজকাল স্কুলের শিক্ষার্থীরাও রোবট বানায়, আর রোবটের ফুটবল খেলা, ‘মেইজ’ বা ধাঁধার পথ পাড়ি দেওয়া কিংবা ড্রোন দিয়ে কোনো কাজ সফলভাবে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে হামেশা হচ্ছে।
নাসা রোবট প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর বুয়েট, ঢাবি আর এনএসইউর মতো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দলগুলো প্রাথমিকভাবে বাছাই হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মূল পর্বে অংশগ্রহণ করছে এবং ভালো করছে।
গ্রামের যে ছেলে নিজের উদ্যোগে একটি হালকা বিমান আকাশে উড়িয়েছিল, তাকে খাটো করছি না। কিন্তু ছোট আকারের একটি বিমান আকাশে ওড়ানো বাচ্চাদের কাজ। খেলনা কোম্পানিগুলো আরও সুচারুরূপে তা করছে। আসল বিমান বানাতে পারে পৃথিবীতে মাত্র তিন-চারটি দেশ আর কোম্পানি।
তবে তার ক্ষেত্রে প্রশংসা করতে হবে এই বলে যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এত দূর সাফল্য সত্যিই অভাবনীয়। কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়। আমাদের ‘ধোলাইখালে’ নাকি পৃথিবীর এমন কোনো যন্ত্র নেই, যা নকল হয় না।
কয়েক বছর আগে একবার টিভিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতকে ধোলাইখালের কারিগরদের প্রশংসা করতে দেখেছিলাম। নিঃসন্দেহে এই কারিগরেরা মেধাবী ও উপযুক্ত সুযোগ পেলে হয়তো আরও ভালো কিছু করতে পারতেন।
বুয়েটকে সরকার একটি দায়িত্ব দিয়েছিল, তথাকথিত ব্যাটারিচালিত রিকশার একটি গ্রহণযোগ্য নকশা করে দিতে। কেননা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভিন্ন নকশায় এটি বানানো হচ্ছিল, যা দুর্ঘটনাপ্রবণ তথা ঝুঁকিপূর্ণ। বুয়েট তা করেছে। তার মানে এই নয় যে বুয়েট শুধু রিকশা বানায়। রিকশা বা গাড়ি বানানো তাঁদের কাজ নয়; বরং এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ।এটাও সত্য যে মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীরা তাঁদের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর বাস্তব জ্ঞান রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মূলত প্রয়োজনে সরকার তথা ইন্ডাস্ট্রিকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যেমন পদ্মা সেতু নির্মাণে মূল পরামর্শক কমিটিতে ছিলেন ছয়জন দেশখ্যাত বুয়েট অধ্যাপক। দেশের প্রায় সব উঁচু দালানেরই নকশায় কোনো না কোনো বুয়েট শিক্ষক জড়িত। জটিল কোনো কারিগরি সমস্যা, সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম বানাতে এখনো বুয়েটের দ্বারস্থ হতে হয়।
তবে বুয়েটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, ভালো মানের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা, আর সে কাজ তারা ভালোভাবেই করছে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন বুয়েটের গ্র্যাজুয়েটরা, আর তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেকে বিশ্বখ্যাত।
যেমন নব্বইয়ের দশকে একবার পত্রিকার প্রথম পাতায় খবর বেরিয়েছিল, বুয়েট গ্র্যাজুয়েট যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুততম হেলিকপ্টার নির্মাণের জনক। সাম্প্রতিক সালেও নাসা থেকে আরম্ভ করে বোয়িং, রোলস রয়েস কিংবা সিলিকন ভ্যালি—সব জায়গাতেই পাবেন বুয়েট গ্র্যাজুয়েট কিংবা বাংলাদেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েট প্রকৌশলীদের।
বুয়েটের পরবর্তী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান যথা চুয়েট, রুয়েট, কুয়েটসহ আর সব পাবলিক কিংবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অনেক মেধাবী প্রকৌশলে ডিগ্রি অর্জন করছেন এবং দেশ-বিদেশে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।
বিশ্বের সর্বোচ্চ ইমারতের নির্মাতা বাংলাদেশি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবেও পাবেন তাঁদের। নিজের কথাই বলি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম ১৯৯৭ সালে। একই বাসায় থাকতাম কয়েকজন। তাঁদের অনেকেই বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তাঁদের মধ্যে তাহের আর কামরুজ্জামান আছেন ‘বোয়িং’–এ, রিচি প্রসাদ মিস্ত্রি আছেন ‘রোলস রয়েস’ কোম্পানিতে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা মিলিয়ে এক ব্যাচে শুধু আমার বিভাগ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আছেন এক ডজনের মতো।
তবে আমাদের মতো যাঁরা দেশে ফিরে এসেছেন, তাঁদের গবেষণার মাত্রা আর জৌলুশ হয়তো প্রবাসীদের মতো নয়। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রও ব্যর্থ হয়েছে বিদেশফেরতদের মেধার সদ্ব্যবহার করতে।
অন্যদিকে ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট কারা এবং তাঁদের ভূমিকা কী? অনেকেই হয়তো জানেন না যে ‘ডিপ্লোমা’ পড়ার জন্য যে ভর্তি পরীক্ষা হয়, তাতে ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে এসএসসি পাস, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়াদের চেয়ে শুরুতেই দুই বছরের কম বিদ্যা।
সর্বোপরি বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কখনোই এসএসসিতে খুব ভালো ফলধারী কেউ এইচএসসি না পড়ে শখ করে ডিপ্লোমা পড়তে যায় না।
তবে হ্যাঁ, কম মেধাবীরা অহেতুক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য কোনো নিম্নমানের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি না নিয়ে এই ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট কোর্সটি করা অনেক যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।
শুধু তা–ই নয়, পারলে এর নিচের স্তরে ‘টেকনিশিয়ান’–এর সংখ্যাও আরও বাড়ানো প্রয়োজন, যাঁরা দেশে–বিদেশে প্রায়োগিক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন।
কিন্তু সমস্যাটি হয় তখনই, যখন এ ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্টরা নিজেদের জন্য অযৌক্তিকভাবে নিজের যোগ্যতার অধিক সুবিধাদি দাবি করে বসেন। ইন্টারনেটের এ যুগে তাঁদের এটি না জানার কথা নয় যে ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট পেশাটি শুধু বাংলাদেশেই প্রথম নয়, যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবীতেই সরাসরি এই নামে অথবা অন্য কোনো নামে আছে।
পৃথিবীর কোথাও আপনি সে দেশে ডাক্তার কিংবা প্রকৌশলী হিসেবে নিবন্ধিত না হলে রোগী দেখতে পারবেন না কিংবা বাড়ি বানানোর ডিজাইনে স্বাক্ষর করতে পারবেন না। কেননা এর সঙ্গে মানুষের জীবন-মরণ জড়িত বিধায় কঠোর আইনের অধীন পরিচালিত। এ ক্ষেত্রে যিনি ডাক্তার কিংবা প্রকৌশলী নন, তিনি যত অভিজ্ঞই হোক না কেন কোনো দিন ডাক্তারের কাজ করতে পারবেন না কিংবা বাড়ির ডিজাইনে স্বাক্ষর করতে পারবেন না, এটাই সারা বিশ্বে স্বীকৃত রীতি।
সারা বিশ্ব, কারিগরি পেশার সর্বোচ্চ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালায়েন্স (আইইএ) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কারিগরি পেশায় তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করে এ পেশায় পড়াশোনা ও কর্মপরিধির জন্য তিন ধরনের নীতি প্রণয়ন করে রেখেছে।
এই তিন স্তরের সর্বোচ্চটি হচ্ছে পেশাদার ‘প্রকৌশলী’দের জন্য, যা ‘ওয়াশিংটন অ্যাকর্ড’–এর আওতাধীন নিয়ন্ত্রিত। দ্বিতীয় স্তরটির ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তাঁদের বলা হবে ‘ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিস্ট’ এবং তাঁরা পরিচালিত হবেন ‘সিডনি অ্যাকর্ড’–এর আওতায়।
তৃতীয় স্তরটিকে বলা হয়েছে ‘ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিশিয়ান’ এবং তাঁরা পরিচালিত হবেন ‘ডাবলিন অ্যাকর্ড’–এর আওতাধীন। এখানে তিনটি স্তরের কারিগরি পেশাজীবীদের কে, কী নামে পরিচিত হবেন, তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে।
অথচ বাংলাদেশের ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্টরা প্রায়ই নিজেদের ‘প্রকৌশলী’ হিসেবে দাবি করেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।
শুধু ইঞ্জিনিয়ারিংই নয়, কৃষি ও মেডিকেল শিক্ষায় একই ধরনের কয়েকটি পর্যায় বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বিদ্যমান ও সরকারি চাকরিতে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের সুবিধাদি দেওয়া হয়ে থাকে।
যেমন ডাক্তারি পেশা ‘মেডিকেল টেকনোলজিস্ট’ কিংবা ‘এলএমএফ ডাক্তার’–এর একটি স্তর আছে। আপনি জীবনে কখন শুনেছেন কি না, এই মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কিংবা এলএমএফ ডাক্তাররা প্রমোশন পেয়ে কখনো ‘মেডিকেল অফিসার’ পদে নিয়োগ পেয়েছেন?
এবার কৃষি পেশায় আসেন। ‘ডিপ্লোমা কৃষিবিদ’ বলে একটি স্তর আছে কৃষি পেশায়। সরকারি চাকরিতে তারা ‘ব্লক সুপারভাইজর’ হিসেবে নিয়োগ পান। তাঁদের কাউকেও আজ পর্যন্ত আমি ‘উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা’ হিসেবে পদোন্নতি পেতে দেখিনি! কৃষিবিদদের কথা বাদ দিলে ডাক্তারি কিংবা প্রকৌশল—দুটি পেশাই অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
ডিপ্লোমা প্রকৌশলী
ডিপ্লোমা প্রকৌশলীছবি: সংগৃহীত
পৃথিবীর কোথাও আপনি সে দেশে ডাক্তার কিংবা প্রকৌশলী হিসেবে নিবন্ধিত না হলে রোগী দেখতে পারবেন না কিংবা বাড়ি বানানোর ডিজাইনে স্বাক্ষর করতে পারবেন না।
কেননা এর সঙ্গে মানুষের জীবন-মরণ জড়িত বিধায় কঠোর আইনের অধীন পরিচালিত। এ ক্ষেত্রে যিনি ডাক্তার কিংবা প্রকৌশলী নন, তিনি যত অভিজ্ঞই হোক না কেন কোনো দিন ডাক্তারের কাজ করতে পারবেন না কিংবা বাড়ির ডিজাইনে স্বাক্ষর করতে পারবেন না, এটাই সারা বিশ্বে স্বীকৃত রীতি।
হ্যাঁ, তিনি তাঁর যোগ্যতার বলে বেশি বেতন দাবি করতে পারেন, হাসপাতালের মালিক হতে পারেন কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে উদ্যোক্তা হতে পারেন—তাঁর জন্য এ ধরনের অনেক পথ খোলা আছে।
বিশেষ করে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্টরা পরবর্তী সময়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করে ডিগ্রি প্রকৌশলী হতে পারেন। অতঃপর একজন প্রকৌশলীর জন্য প্রযোজ্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন।
কিন্তু আফসোসের বিষয়, দেশে বিভিন্ন সময়ে যখন ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্টরা আন্দোলনে নামেন, সরকার ‘ভোট বেশি’—এ বিবেচনায় নিয়ে তাঁদের পক্ষ অবস্থান নিয়ে একের পর এক অন্যায্য দাবি মেনে নিয়েছে। ৩৩ শতাংশ কোটায় পদোন্নতি পেয়ে তাঁরা সহকারী প্রকৌশলী হয়ে যাবেন, এটা তেমনি একটি আইন।
আমার ভয় হয় যে এটি অনুসরণ করে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কিংবা এলএমএফ ডাক্তাররাও একসময় আন্দোলনে নামবেন এই বলে যে মেডিকেল অফিসার পদে তাঁদের মধ্য থেকে যেন ৩৩ শতাংশ পদোন্নতি দিয়ে পূরণ করা হয়।
একইভাবে ১০ম গ্রেডে ‘উপসহকারী প্রকৌশলী’ পদে শুধু ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্টরা ১০০ শতাংশ নিয়োগ পাবেন, ডিগ্রি প্রকৌশলীরা সেখানে আবেদন করতে পারবেন না, এটাও যৌক্তিক নয়। এটা একটি সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন যে একজন এমএ পাস প্রার্থী সর্বদাই একটি বিএ পাসের চাকরির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।
হ্যাঁ, একসময় স্কুলে বিজ্ঞান কিংবা কারিগরি শিক্ষক হিসেবে ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্টদের নিয়োগের একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অজ্ঞাত কারণে তা স্থগিত হয়। সম্ভবত বিএ পাস স্কুলশিক্ষকেরা তাঁদের গ্র্যাজুয়েট নন বলে দাবি করে আন্দোলন করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি বরং এটিকে যৌক্তিক মনে করি যে স্কুলশিক্ষক হিসেবে তাঁদের নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।
আমার ধারণা, এতে স্কুল পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটবে। এ ধরনের যৌক্তিক দাবির পক্ষে অথচ ডিপ্লোমাদের খুব শক্ত অবস্থান লক্ষ করিনি; বরং আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নেওয়ার মতো তাঁরা ডিগ্রি প্রকৌশলীদের সঙ্গে বরাবর অযৌক্তিক তর্ক আর অন্যায্য দাবি জানিয়ে আসছেন।
বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশের উন্নয়নের জন্য বিশাল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা আশু প্রয়োজন। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন মেনে, যে যার সঠিক অবস্থানে থেকে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন, এটাই কাম্য।
ড. মো. সিরাজুল ইসলাম অধ্যাপক, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও পরিচালক, সেন্টার ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভিসেস (সিআইআরএস), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।