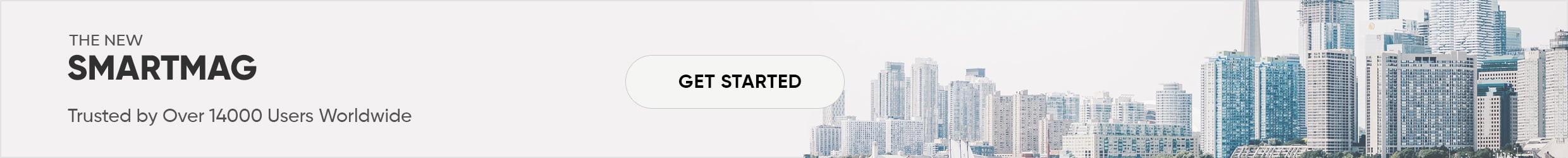নির্বাচনের একটি নির্দিষ্ট সময় ঘোষণার পর অনেকেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। ‘ফেলেছিলেন’ বলছি; কারণ, ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে নির্বাচনের মাস ঘোষণার সপ্তাহ তিনেক না যেতেই সেই ‘স্বস্তি’ অনেকটাই হারিয়ে গেছে। বিষয়টি এমন নয় যে নির্বাচনের ঘোষিত সময়সীমা থেকে সরকার বা প্রধান উপদেষ্টা সরে এসেছেন।
প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার সূত্রে এখন পর্যন্ত এটা আমাদের জানা যে নির্বাচন হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে আর তফসিল হবে এ বছরের ডিসেম্বরে। প্রশ্ন হচ্ছে, এরপরও নির্বাচন নিয়ে মানুষের মনে এত সংশয় কেন? সবাই কেন এটা জানতে চায়, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে তো?
প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের সময় ঘোষণার পর রাজনৈতিক দলগুলো যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তাতে মাত্রাগত পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুলের প্রতিক্রিয়া ছিল এ রকম, ‘এই ঐতিহাসিক ঘোষণায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা কেটে যাবে, গণতন্ত্র উত্তরণের পথকে সুগম করবে।’
নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা নিয়ে বিএনপির এ উচ্ছ্বাস অন্য দলগুলোর মধ্যে দেখা যায়নি। জামায়াত ‘যদি’, ‘কিন্তু’সহ নির্বাচনের সময় ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিল। তারা জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন, সনদের আইনি ভিত্তি এবং তা সংবিধানে যুক্ত করার কথা বলেছে। এনসিপির নেতাদের প্রতিক্রিয়া ছিল বেশ শীতল। তারা বলেছে, শুধু একটি নির্বাচনের জন্য গণ-অভ্যুত্থান হয়নি। নির্বাচনের আগে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা এবং সংস্কার ও বিচারের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি নিশ্চিতের দাবি তোলে তারা। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগের দাবিও রয়েছে তাদের।
ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান ছিল আরেকটু নেতিবাচক। তারা বলেছিল, দেশে এখনো নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়নি। তাদের পক্ষে নির্বাচনে যাওয়া কঠিন বলেও তখন মন্তব্য করেছিলেন দলটির আমির। সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবি থেকে যে তারা সরছে না, সেটাও তখন তারা পরিষ্কার করে দিয়েছিল।
রাজনৈতিক দলগুলোর এসব প্রতিক্রিয়ায় তখনই বোঝা গিয়েছিল যে আরও কিছু কার্ড তারা হাতে রেখে দিয়েছে। এখন নির্বাচনের সময় যত এগিয়ে আসছে, দলগুলো নিজেদের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ অনুযায়ী সেই কার্ডগুলো খেলা শুরু করেছে। সমস্যা হচ্ছে, যেভাবে এবং যে কার্ডগুলো ছাড়া হচ্ছে, তাতে ঘোষিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে শঙ্কা ও উদ্বেগ বেড়ে চলেছে।
বিএনপির চাওয়া ছিল এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন। শেষ পর্যন্ত ’২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগের নির্বাচনের ঘোষণাকেই তারা খুশিমনে মেনে নিয়েছে। অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে দ্রুত নির্বাচন তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। নির্বাচন যত দ্রুত হবে, ফল তত বিএনপির পক্ষে যাবে—এমন একটি ধারণা বেশ প্রতিষ্ঠিত।
২.
এনসিপি নেতাদের এখনকার বক্তব্য এমন মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে যে তাঁরা ঘোষিত সময়ে নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। দলটির এক নেতা তো পরিষ্কার বলেছেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না।’
এটা এনসিপির বক্তব্য বা অবস্থান না হলে দল থেকে অন্তত ব্যাখ্যা পাওয়া যেত। তেমন কিছু আমরা পাইনি। ‘সংস্কার ছাড়া নির্বাচন নয়’ বা ‘নতুন সংবিধানের অধীনে নির্বাচন’—এমন দাবি তোলার অর্থই হচ্ছে ফেব্রুয়ারি ’২৬–এর নির্বাচনকে না বলা। রাজনৈতিক দল হিসেবে এনসিপির জনসমর্থন বা জনভিত্তি কতটা জোরালো, সে পরীক্ষা হয়নি, কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের এই নতুন দলটির রাজনৈতিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই।
এনসিপির নির্বাচনবিরোধী অবস্থানকেও তাই হালকাভাবে নেওয়া যাচ্ছে না। তবে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত, বিএনপিকে চাপে রাখা বা আসন ভাগাভাগির ক্ষেত্রে কোনো দলের কাছ থেকে বাড়তি আসন আদায়ের কৌশল হিসেবে দলটি এসব দাবি তুললে অবশ্য ভিন্ন কথা।এনসিপির রাজনৈতিক মিত্র হিসেবে বিবেচিত জামায়াতে ইসলামী অবশ্য এনসিপির মতো সরাসরি ফেব্রুয়ারির নির্বাচনবিরোধী অবস্থান প্রকাশ বা বক্তব্য দিচ্ছে না। তবে দুই কক্ষের সংসদের ব্যাপারে যে রাজনৈতিক ঐকমত্য হয়েছে, সেখানে দলটি দুই কক্ষেই সংখ্যানুপাতিক (পিআর) নির্বাচনের দাবিটি অব্যাহতভাবে তুলে ধরছে।
ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত সংসদ নির্বাচন যে পিআর পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়, তা জামায়াত জানে না, এমন নয়। এ দাবিকে জামায়াত এখনো আগামী নির্বাচনের সঙ্গে শর্তযুক্ত করেনি। সে হিসেবে জামায়াতের এ দাবিকে এখন পর্যন্ত দলের চাওয়া বা আদর্শিক অবস্থান বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে লন্ডন ঘোষণা, জুলাই ঘোষণাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে অন্তর্বর্তী সরকার বিএনপিকেই বিবেচনায় নিচ্ছে বলে মনে করে জামায়াত। এটা নিয়ে দলটির মধ্যে অসন্তোষ ও বিরক্তি রয়েছে।
তবে এনসিপির আরেক সম্ভাব্য রাজনৈতিক সহযোগী ইসলামী আন্দোলন সংসদের দুই কক্ষেই পিআর পদ্ধতির ভোটের জোরালো সমর্থক। পিআর প্রশ্নে তাদের অবস্থান বেশ কঠোর ও অনমনীয়। দলটির আমির গত শুক্রবারও বলেছেন, সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতি ছাড়া আসন্ন জাতীয় নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না। দলটির রাজনৈতিক অবস্থানও এনসিপির মতোই দৃশ্যত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের বিরুদ্ধে।
গণ-অভ্যুত্থানে শরিক সব রাজনৈতিক দলের উচিত হবে ফেব্রুয়ারি ’২৬–এর নির্বাচনকে দলীয় স্বার্থের ওপরে জায়গা দেওয়া। নির্বাচনটিকে জাতীয় স্বার্থ হিসেবে বিবেচনা করে এ ক্ষেত্রে সব অনিশ্চয়তা দূর করার উদ্যোগ নেওয়া।
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক মেরুকরণে অনেকেই এনসিপি, জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনকে কিছুটা এক কাতারের শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেন। যদিও শেষ পর্যন্ত এই মেরুকরণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা বলা কঠিন। দেখা যাচ্ছে, এই তিন দলের মধ্যে এনসিপি ও ইসলামী আন্দোলন (দল দুটির ভেতরে যা চিন্তাভাবনাই থাক না কেন) অন্তত প্রকাশ্যে বেশ শক্তভাবে নির্বাচনবিরোধী অবস্থান প্রকাশ করে যাচ্ছে। মাঝামাঝি অবস্থানে আছে জামায়াতে ইসলামী। সবকিছু মিলিয়ে নির্বাচন নিয়ে তিনটি দলের বিভিন্ন শর্ত তুলে ধরার চেষ্টা ফেব্রুয়ারি ’২৬–এর নির্বাচন নিয়ে জনমনে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।
বিএনপির চাওয়া ছিল এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন। শেষ পর্যন্ত ’২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগের নির্বাচনের ঘোষণাকেই তারা খুশিমনে মেনে নিয়েছে। অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে দ্রুত নির্বাচন তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। নির্বাচন যত দ্রুত হবে, ফল তত বিএনপির পক্ষে যাবে—এমন একটি ধারণা বেশ প্রতিষ্ঠিত।দলটিও মনে করে, ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে তারাই বিজয়ী হবে। জুলাই সনদ বা সংস্কারসহ বিভিন্ন উদ্যোগে তাদের অবস্থানই প্রমাণ করে যে তারা নিজেদের ভবিষ্যতের ক্ষমতাসীন দল হিসেবে বিবেচনা করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হলে বিএনপি ক্ষমতায় যাবে—এ বিবেচনা থেকেই কি কোনো পক্ষ নির্বাচনকে অনিশ্চিত করে তুলতে চাইছে?
গণ-অভ্যুত্থান বা বড় যেকোনো পরিবর্তন নানা শক্তিকে রাজনীতিতে সক্রিয় ও তৎপর হওয়ার সুযোগ করে দেয়। নৈরাজ্যবাদ বা হঠকারিতা—এগুলো রাজনীতিরই ধারা ও পথ। ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ ধরনের শক্তি নানাভাবে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হিসেবে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, এমনকি অন্তর্বর্তী সরকারকেও নানাভাবে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।
আবার গণ-অভ্যুত্থানে পতিত রাজনৈতিক শক্তিও নানা কায়দায় নিজেদের অবস্থান জোরদারের চেষ্টা করছে। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগ নেতারা সেখানে বসেই দলের কৌশল সাজাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। রাজনীতির জল যত ঘোলা হবে, এসব শক্তির মাছ শিকার করতে তত সুবিধা হবে।
৩.
অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার এরই মধ্যে এক বছর পার করেছে। দীর্ঘ ১৬ বছরের স্বৈরশাসন ও রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের পর সরকার পরিচালনার কাজটি সহজ ছিল না। এই সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতার হিসাব-নিকাশ যা–ই হোক না কেন, নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর যে জরুরি হয়ে পড়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে সময় ঘোষণা করা হয়েছে, তা থেকে সরে আসার কোনো পথ আছে বলে মনে হয় না।
গণ-অভ্যুত্থানে শরিক সব রাজনৈতিক দলের উচিত হবে ফেব্রুয়ারি ’২৬–এর নির্বাচনকে দলীয় স্বার্থের ওপরে জায়গা দেওয়া। নির্বাচনটিকে জাতীয় স্বার্থ হিসেবে বিবেচনা করে এ ক্ষেত্রে সব অনিশ্চয়তা দূর করার উদ্যোগ নেওয়া।
নিজেদের ভবিষ্যতের ক্ষমতাসীন দল বিবেচনা করে গণতান্ত্রিক সংস্কারে ছাড় না দেওয়া বা কোনো একটি দলের ক্ষমতায় আসা ঠেকাতে নির্বাচনকে অনিশ্চিত করে ফেলা—দুটি পথই আত্মঘাতী। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ হিসাব করতে হবে যে নির্বাচন অনিশ্চয়তার মুখে পড়লে আসলে কার লাভ? বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হোক, এটা কোন শক্তি বা কারা চাইবে না?
এ কে এম জাকারিয়া প্রথম আলোর উপসম্পাদক
akmzakaria@gmail.com
*মতামত লেখকের নিজস্ব