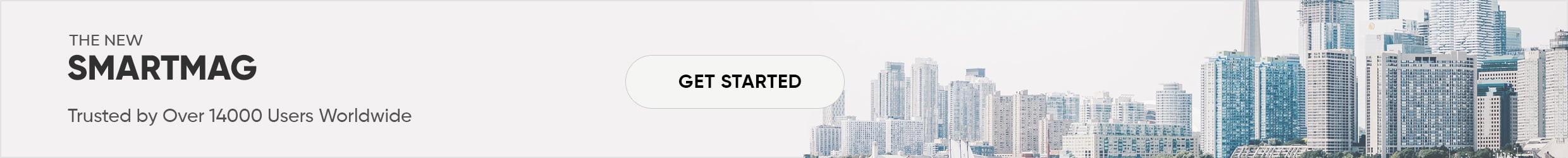উপমহাদেশে ইসলামি জ্ঞানচর্চার বিকাশ, বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রচার এবং সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রয়েছে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তার নাম মাদ্রাসা–ই রহিমিয়া।
হানাফি ফিকহের সাড়াজাগানো গ্রন্থ ফতোয়ায়ে আলমগীরি সংকলন কাজে অবদান রাখেন এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। উপমহাদেশে হাদিসের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের (কুতুবে সিত্তা) পাঠদান চালু করেন এই মাদ্রাসার প্রাণপুরুষ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রথম ঘোষক এই মাদ্রাসার সফল অধ্যক্ষ। সে হিসেবে মাদ্রাসা রহিমিয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।
১৭০০ সালের দিকে দিল্লির মেহেন্দিয়ান এলাকায় এই মাদ্রাসার গোড়াপত্তন হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ আবদুর রহিম দেহলভি (রহ.)। তাঁর নামে মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ আলেম, শাস্ত্রীয় পণ্ডিত ও বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব। সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের সমসাময়িক ছিলেন।
তাঁর জ্ঞানের গভীরতার কথা জানতে পেরে সম্রাট আলমগীর তাঁকে মজলিস-ই-আলমগীরির সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিত করেন, যাঁদের প্রধান কাজ ছিল ফতোয়ায়ে আলমগীরি সংকলন কাজে দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন করা। তিনি এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
বিদ্বান পিতা তাঁকে কোরআন, হাদিস, ফিকহ, ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে শাহ ওয়ালিউল্লাহ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন।শাহ আবদুর রহিম দেহলভির জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি। পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি এই মাদ্রাসায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বিদ্বান পিতা তাঁকে কোরআন, হাদিস, ফিকহ, ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেন। ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করে মাত্র ১৫ বছর বয়সে শাহ ওয়ালিউল্লাহ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন।
এরপর তিনি পিতার কাছ থেকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করে এখানে শুরু করেন শিক্ষকতা। ১৭১৮ সালের শেষের দিকে মৃত্যুবরণ করেন তাঁর সম্মানিত পিতা। তারপর তিনি এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হন।
জ্ঞানের পিপাসায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি ছিলেন কাতর। এ জন্য ৩০ বছর বয়সে হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন তিনি। প্রখ্যাত আলেম ও হাদিসবিশারদ শাইখ আবু তাহের বিন ইব্রাহিম আল-কুর্দি আল-মাদানি (রহ.)-এর কাছ থেকে হাদিস ও ফিকহের উচ্চতর সনদ লাভ করেন। সেখানে তিনি আট বছর অবস্থান করে নিজের মেধামননকে শাণিত করে তোলেন।
হাদিস বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিল অতুলনীয়। তাই দেশে ফিরে নিজ মাদ্রাসায় কুতুবে সিত্তার সমন্বয়ে চালু করেন হাদিসের বিশেষায়িত পাঠদান। তখন থেকে তিনি বরিত হন ‘মুহাদ্দিসে দেহলভি’ (দিল্লির মুহাদ্দিস) উপাধিতে।শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) মাদ্রাসা রহিমিয়াকে কেন্দ্র করে শুরু করেন বৈপ্লবিক মিশন। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি করেন মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম। হাদিসে কুতুবে সিত্তা ও উলুমুল হাদিসের পাঠ, তাফসিরে কোরআনের অনুবাদ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উসুলুস তাফসির, ফিকহে হানাফি মাজহাবের ভিত্তিতে মাসআলা উদ্ভাবন ও ফতোয়া প্রদান, আকিদায় ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির শিক্ষা, যুক্তিবিদ্যায় ইসলামি দর্শনের ধারণা ও গ্রিক দর্শনের সমালোচনা, সাহিত্যে আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন এবং আত্মশুদ্ধিতে নকশবন্দি তরিকায় আত্মিক উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেন।
সেই সঙ্গে সমাজ সংস্কারমূলক শিক্ষা ও কাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। এর মাধ্যমে তিনি এমন একদল শিষ্য ও অনুসারী গড়ে তোলেন, যাঁরা তাঁর বৈপ্লবিক মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) মাদ্রাসা রহিমিয়াকে কেন্দ্র করে শুরু করেন বৈপ্লবিক মিশন। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি করেন মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম।
পাঠদানের পাশাপাশি তিনি লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ফাতহুর রহমান নামে কোরআনের ফার্সি অনুবাদ করেন।
উল্লেখ্য, সে সময় ফার্সি ছিল উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা। তাফসিরের মূলনীতি ও ব্যাখ্যা নিয়ে আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত তাফসির; ইসলামি আইন, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা; খেলাফতের ইতিহাস ও রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা; আত্মশুদ্ধি ও সুফিবাদ নিয়ে আল-কাওলুল জামিল; আধ্যাত্মিক ভাবনা ও দর্শন নিয়ে আত-তাফহিমাতুল ইলাহিয়া; হেজায সফরের অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নের বর্ণনা নিয়ে ফুয়ুজুল হারামাইন এবং ইমাম মালেক (রহ.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ মুয়াত্তার ব্যাখ্যা লিখেন শরহে মুয়াত্তা নামে। এ ছাড়া আরও অসংখ্য গ্রন্থ-পুস্তক রচনা করেন তিনি।
১৭৬২ সালে মৃত্যুবরণ করেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)। তারপর মাদ্রাসা রহিমিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আজিজ দেহলভি। তিনি এই মাদ্রাসায় পিতার সযত্ন তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ফলে শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার, চিন্তাধারা ও আদর্শের মানদণ্ডে তিনি হয়ে ওঠেন পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি।
শাহ আবদুল আজিজ দেহলভি (মৃ. ১৮২৪)
শাহ আবদুল আজিজ দেহলভি (মৃ. ১৮২৪)ছবি: উইকিপিডিয়া
কোরআনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর। ফাতহুল আজিজ নামে একটি তাফসির রচনা করেন। হাদিস বিষয়ে বুস্তানুল মুহাদ্দিসিন ও ইজালাতুন নাফিয়া নামে দুটি গ্রন্থ লিখেন। ইসলামি আইন বিষয়ে রচনা করেন আল-ফাতওয়া ফিল মাসাইলিল মুশকিলা। এ ছাড়া তিনি উসুল, যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস-ভূগোল, কবিতা ও বক্তৃতায় নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ফলে আলেমসমাজ তাঁকে ভূষিত করেন ‘সিরাজুল হিন্দ’ (হিন্দুস্তানের সূর্য) উপাধিতে।শাহ আবদুল আজিজ দেহলভি (রহ.) ৬০ বছরের বেশি সময় মাদ্রাসা রহিমিয়ার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে মাদ্রাসার সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে জামে মসজিদের পাশে মাদ্রাসার জন্য জায়গা বরাদ্দ দেন। সেখানে নির্মিত হয় বিশাল ভবন। তিনি মাদ্রাসায় বিভিন্ন বিভাগ গড়ে তোলেন। প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবারে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে তাফসির মজলিস করেন। সেই সঙ্গে হাদিসের পাঠদান, ফতোয়া প্রদান ও আধ্যাত্মিক সাধনা চালিয়ে যান। এসব কাজে তাঁকে সহায়তা করেন তাঁর দুই ভাই-শাহ রফিউদ্দিন ও শাহ আবদুল কাদির।
১৮০৩ সালে ব্রিটিশরা দিল্লি দখল করে সবখানে ব্যাপক অরাজকতা চালায়। তিনি তখন দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘হিন্দুস্তান এখন দারুল হরব (যুদ্ধকবলিত দেশ)। তাই সবার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ফরজ।’
সে সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দিল্লির অবস্থা ছিল বিপর্যস্ত। মোগল সাম্রাজ্যের ক্রান্তিকাল চলছিল। এই সুযোগে ১৮০৩ সালে ব্রিটিশরা দিল্লি দখল করে সবখানে ব্যাপক অরাজকতা চালায়। তিনি তখন দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘হিন্দুস্তান এখন দারুল হরব (যুদ্ধকবলিত দেশ)। তাই সবার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ফরজ।’ তাঁর ওই ঐতিহাসিক ঘোষণা গোটা উপমহাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে।
ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অগ্রসেনানী হিসেবে তৈরি হয়ে যায় তাঁরই হাতেগড়া শিষ্যদের একটি কাফেলা, যাদের প্রধান ছিল সাইয়েদ আহমদ শহিদ (রহ.) এবং তাঁর সিপাহসালাত ছিলেন শাহ ইসমাইল শহিদ (রহ.)। ১৮৩১ সালে বালাকোটে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁরা শহিন হন।
১৮২৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন শাহ আবদুল আজিজ দেহলভি (রহ.)। তারপর এই মাদ্রাসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর আদরের দৌহিত্র শাহ ইসহাক দেহলভি (রহ.)। তিনি শ্রদ্ধেয় নানাজানের জ্ঞান ও সম্পদের উত্তরাধিকারী হন। তাঁর অনুকরণে কোরআন-সুন্নাহর পাঠদান চালিয়ে যান। কিন্তু ব্রিটিশরা এই মাদ্রাসাকে সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি মনে করে তার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এ কারণে তিনি ১৮৪২ সালে হিজরত করে মক্কায় চলে যান।
তারপর ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পর ব্রিটিশরা মাদ্রাসা দখল করে নেয়। তারা ভবনগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। এরপর যা কিছু বাকি ছিল, তা রামজি দাস নামক এক হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। তিনি একে গুদামঘরে পরিণত করেন। এভাবে সমাপ্ত হয় মাদ্রাসা রহিমিয়ার ঐতিহাসিক অধ্যায়।