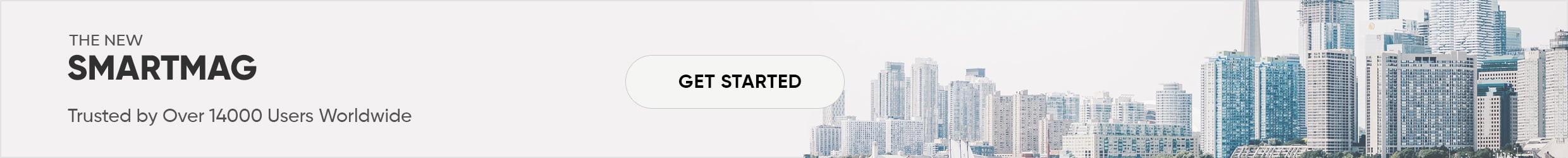কয়েকদিন পরেই ২১, বাংলা ভাষা আন্দোলনের এক মূর্ত প্রতীক। ওটা স্বীকৃতির বিষয়। আবার ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব এখনও কাটেনি। সামান্য তারতম্যে বিপদও ঘটে যেতে পারে।
——————————————————
 ‘Left’ শব্দটা যে এমন বিপত্তিতে ফেলবে তা আগে ভাবিনি। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জেনেছি শব্দটা শুনলে তামাম দুনিয়ার সঙ্কীর্ণতাবাদী মানুষজন শিউরে ওঠেন—অনেকে অবার সবকিছুতেই ‘Left ভূতদের’ আবিষ্কার করে থাকেন। কিন্তু সেই ‘Left’ ইংরেজিতে বিশেষ্য থেকে ক্রিয়াপদ হয়ে একটি পরিবারকে সাময়িক বিপর্যয়ে ফেলবে তা আগে কখনও ভাবিনি।
‘Left’ শব্দটা যে এমন বিপত্তিতে ফেলবে তা আগে ভাবিনি। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জেনেছি শব্দটা শুনলে তামাম দুনিয়ার সঙ্কীর্ণতাবাদী মানুষজন শিউরে ওঠেন—অনেকে অবার সবকিছুতেই ‘Left ভূতদের’ আবিষ্কার করে থাকেন। কিন্তু সেই ‘Left’ ইংরেজিতে বিশেষ্য থেকে ক্রিয়াপদ হয়ে একটি পরিবারকে সাময়িক বিপর্যয়ে ফেলবে তা আগে কখনও ভাবিনি।
ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছরের ডিসেম্বরে। স্থান হায়দরাবাদ। শিক্ষকদের সর্বভারতীয় প্রশিক্ষণ সংস্থায় দশদিনের একটি কর্মশালায় গিয়েছি। ৪৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি একমাত্র আমি। হস্টেলে প্রতি ঘরে তিনজন আছেন—আমার ঘরে বাকি দুইজনের একজন ড. রামচন্দ্র পান্ডে—নিবাস অযোধ্যা, কর্মস্থল যমুনোত্রী। দ্বিতীয়জন ভি কার্তিক, নিবাস তামিলনাডু। সেই-ই এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র।
রবিবার, প্রায় সব শিক্ষার্থীরা গিয়েছেন ফিল্ম সিটিতে। রয়ে গিয়েছেন তামিলনাডুর ৭ জন, একজন বাঙালি। ওঁরা যাননি কারণ সোমবার ওঁদের রাজ্যের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি আছে—তাই সারা দিন মহড়ায় ব্যস্ত। আমি যাইনি কিছু কাজ আছে তাই। দুপুরবেলা মধ্যাহ্ন আহারের পর সেই কাজ সারতে বের হলাম হায়দরাবাদের রাস্তায়। সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখি তামিলরা কেউ নেই, কার্তিকও নেই। ঘরের চাবি তাঁরই কাছে। অগত্যা ফোন।
এখানেই বাধল গোল। কার্তিকের যে নম্বরটি পেলাম সেটি রিডাইরেক্ট করা তাঁর বাড়িতে। ফোন করতেই ওপ্রান্তে মহিলার কণ্ঠস্বর। প্রথমে হিন্দি, পরে ইংরেজিতে বোঝানোর চেষ্টা করলাম সমস্যাটা। ও প্রান্তের মহিলা বলছেন ‘নো ইংলিশ, ওনলি তামিল’, তামিল আমার আসে না—চারপাশের মানুষজন যাঁরা হিন্দি বোঝেন তাঁদের সমস্যাটা বুঝিয়ে মহিলাকে তামিলে সমস্যাটা বলার অনুরোধ করলাম। তাঁদের আবার হিন্দি আসে, তেলেগু আসে—তামিল আসে না। শেষমেশ এগিয়ে এলেন এক পাঞ্জাবি। তিনি জানালেন, তামিল না জানলেও ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি তাঁর কাছে আছে। শর্ত, বাকি রুমমেটরা না ফেরা পর্যন্ত ঘরেই থাকতে হবে।
ঘরে তো ঢুকলাম। এবার বাধল অন্য বিপত্তি। নানা নম্বর থেকে ফোন আসছে—ওপাশে কান্নাকাটির শব্দ আর তাঁরা দুর্বোধ্য তামিলে নানা প্রশ্ন করছে—আমি বলতে চাইছিলাম—‘Kartick, my roommate in CCRT has left the hostel with the room key. I am waiting for him’। এতে কান্নাকাটির কী থাকতে পারে তা বুঝতে পারছি না।
রাত নটা—সবাই ফিরে এসেছেন। তামিল বন্ধুদের একজন যিনি একমাত্র হিন্দি যানেন তিনি এলেন, প্রশ্ন করলাম কার্তিক কোথায়? বললেন—‘খুব খারাপ ব্যাপার। কার্তিকের ফোনে চার্জ ছিল না। ওঁরা বাজারে গিয়েছিলেন। সে সময় কেউ কার্তিককে ফোন করে। ফোন যায় ওঁর স্ত্রীর কাছে সে মহিলাকে বলে যে—‘কার্তিক মারা গেছে।’
আমি বাক্রুদ্ধ—কার্তিক আর Left দুটো শব্দকে এক করে এমন অদ্ভুত মানে হতে পারে তা সত্যিই ভাবিনি। পরিবারের সবাইকে নিশ্চিন্ত করে কার্তিক ঘরে ফিরে এলে তাকে সবটা বলার পর সারা হস্টেলে হাসির ধুম পড়ে গেল। কার্তিক তাঁর স্ত্রীকে তামিলে কি সব বলছিল—তার একটারও মানে বুঝিনি। তবে বুঝেছিলাম বিষয়টা নিয়ে ওঁদের বাড়িতেও ঠাট্টা মস্করা শুরু হয়ে গিয়েছে।
প্রশ্ন ও প্রান্তের মহিলার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? তিনি স্নাতক ও প্রাথমিক শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। অতএব কোনও অর্থেই তাঁকে অশিক্ষিত বলা যাবে না। তবে জনৈক তামিল শিক্ষকের মুখে শুনলাম ওখানকার রাজ্য সরকারের সব স্কুলে কেবলমাত্র তামিল শেখানো হয়। অন্য কোনও ভাষা নয়। ইংরেজি ক্লাস সিক্স থেকে। কাজেই এই সমস্যা কেবলমাত্র সর্বভারতীয় বোর্ডে যাঁরা পড়েন তাঁরা হিন্দি ও ইংরেজি শেখার সুযোগ পান।
পশ্চিমবঙ্গের অনেক নাক উঁচুদের একটা কথা বলতে শুনেছি, তামিলনাডুর অটোচালকরাও ইংরেজি জানেন—আর ৩৪ বছরের ‘লাল’ শাসন নাকি বাঙালিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে সেই ইংরেজি জ্ঞানেরও প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল ভেলোরে। সেখানে ১০ জন যাত্রীর, ৬ জনই বাঙালি। অটোচালক তামিল। শুদ্ধ ইংরেজিতে ভাড়া জিজ্ঞাসা করায় জবাব পেলাম না। তারপর একজন সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন — ‘How much?’ দেব অটোর ভাড়া, তারসঙ্গে How much এর কি সম্পর্ক ভাবছি কিন্তু জবাব এল ঠিকঠাক। দরাদরি চলছে, সহযাত্রী একটি দর বললেন—অটোচালক নারাজ। সহযাত্রী একটু হেঁকে বলে উঠলেন ‘Go to go, no go to no go.’ অটোচালক রাজি হয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য, নিরাপদে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এ হলো তামিল সাধারণ জনতার ইংরেজি জ্ঞানের হাল।
তামিলদের আরেকটি গপ্পো বলি—সর্বভারতীয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ—কিছু প্রশিক্ষক হিন্দিতে বলছেন তখন তামিলরা চুপচাপ—কিছু বুঝতে পারছেন না। এবার তাঁদের নীরবতায় প্রশিক্ষক বুঝতে পারছেন ভাষাগত সমস্যা। শুরু করছেন ইংরেজিতে। তখন উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ আর গুজরাটের শিক্ষকরা প্রতিবাদে উত্তাল—হিন্দিতেই পড়ানো চলুক। কাজেই প্রতিটি বিষয় একবার হিন্দি আর একবার ইংরেজিতে বলতে হচ্ছে। মিউজিয়াম কিংবা গোলকুণ্ডা দুর্গে ভ্রমণ—দুই ভাষার দুই দোভাষীর ব্যবস্থা। এছাড়া কোনও উপায় নেই—এমনকি দুই দলের মধ্যে ভাষাগত বিভিন্নতা নিয়ে নানা টিকা-টিপ্পনি, সামান্য তিক্ততাও চোখে পড়েছে।
এই কথাটাই শুনেছি বার বার—ভাষা এমন একটা বিষয় যার মাধ্যমে যে কোনও সময়ে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেওয়া যায়। আর সে দেশটার নাম যদি হয় ভারতবর্ষ তাহলে তো কোনও কথাই নেই। যেমন ধরুন ভারতের সংবিধান—২২টি ভাষাকে অষ্টম তফসিলের মধ্যে নেওয়া হয়েছে। ১৯৬১ সালে মাতৃভাষার সংখ্যা? ১৬৫২। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বিবিধ বাচনভঙ্গি। কেবলমাত্র হিন্দিতেই রয়েছে—৪৯টি বাচনভঙ্গি বা ডায়ালেক্ট। তাহলেই বুঝুন। রামচন্দ্রজী বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন, হিন্দিতে নয়—ভোজপুরীতে। উত্তর ভারতে নানা অংশে হিন্দির চেয়ে ভোজপুরী বেশি ব্যবহার করা হয়। গান, কবিতায় ভোজপুরীর প্রয়োগ। সেই ভোজপুরীতে ‘স্ত্রী’ এর বদলে ব্যবহৃত হয় ‘মোতরমা’। শব্দটির উৎস উর্দু। প্রবল মন্দিরপন্থী রামচন্দ্রজী উর্দু শব্দ ব্যবহার করছেন! প্রশ্ন শুনে রামচন্দ্রজী বলেছিলেন, ভোজপুরীতে বহু এমন শব্দ পাওয়া যাবে, তবে তো কোনও সংঘাত থাকার কথা নয়—কিন্তু সংঘাত আছে। সংঘাত থাকবেও। কারণ সবারই ধারণা, তাঁর ভাষাই সবচেয়ে শ্রুতিমধুর—অথচ অন্য কোনও ভাষা তিনি মন দিয়ে শুনেছেন বা বুঝেছেন কী না তা নিয়ে কোনও তথ্য নেই।
ধরা যাক সকালে রাঘববাবু বাজারে যাচ্ছেন—রাস্তায় দেখা যাদববাবুর সঙ্গে। রাঘববাবু সদ্য গুজরাট থেকে ঘুরে এসেছেন। মজা করেই বললেন—‘কেম ছো?’— যাদববাবু বিস্ময়ে হতবাক? রাঘববাবু মজা করেই আবার বললেন ‘কেম ছো?’ তারপর রহস্য ভেঙে বলে উঠলেন—গুজরাটিতে ‘কেম ছো’ মানে ‘কেমন আছো?’ এর উত্তর যদি হয় ভালো তবে বলতে হবে ‘মজামা’। ধরুন কেউ প্রশ্ন করলেন — ‘নীংগল এপাডি ইরুক্কিরংগল?’ কিংবা ‘মীরু এলা উন্নারু?’ তা হলে বঙ্গভাষীদের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে? কিংবা যদি কোনও তামিলকে বলা হয় ‘কেমন আছেন?’ তা হলে আপনি কী জবাব পাবেন।? আসলে বহু ভাষাভাষির এই দেশে ভাষা একটা বড় সমস্যা। একটা রাজ্যের মধ্যেই কতগুলো ভাষা। হিমাচল প্রদেশে ১২টি জেলাতে ব্যবহৃত হয় চারটি আঞ্চলিক ভাষা—কিন্নরি, পাহাড়ী, কাংড়ি ও ডোগরি। এছাড়াও রয়েছে হিন্দি ও পাঞ্জাবি। মহারাষ্ট্রেও মারাঠি ছাড়া রয়েছে কোঙ্কনি, পাওড়ি। জলগাঁও জেলাতে ভীল, পাওড়ি। তঁদভি উপজাতিদের মধ্যে পাওড়ি ভাষা খুব জনপ্রিয়, সে ভাষায় নানা অনুবাদ কর্ম ও মৌলিক সাহিত্যও রয়েছে। ভাষা নিয়ে অনেক ভাসা ভাসা ধারণা রয়ে গিয়েছে যা আসলে আমাদের মনোজগতে নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। সেখান থেকে শুরু হয় নানা কল্পকথা।
সাধারণত আমাদের দেশে একটা অতি প্রচলিত ধারণা হলো দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলি দ্রাবিড় ভাষা। কিন্তু পাকিস্তানের অন্তর্গত বালুচিস্তান ও আফগানিস্তানে ২৪ লক্ষ মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন তা দ্রাবিড় ভাষা—নাম ব্রাহুই। এই ভাষাভাষি মানুষ আরবি লিখনশৈলী ও হরফ ব্যবহার করেন। ইরান ও তুর্কমেনিস্তানে এই ভাষায় কথা বলেন এমন মানুষ পাওয়া যাবে। কুড়ুক ভাষার মধ্যে রয়েছে নয়টি বিভিন্ন ধারা যার মধ্যে ঝাঙ্গুর এর উৎস দ্রাবিড় ভাষা। কাজেই ভাষাগত বৈচিত্র্য কোনও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের মধ্যে আবদ্ধ নেই।
আমাদের দেশেই প্রধানত যে সব ভাষাগুলি ব্যবহৃত হয় তাদের উৎস চারটি—ইন্দো এরিয়ান; দ্রাবিড়; টিবেটো বার্মিজ; ও অস্ট্রো এশিয়াটিক। ভাষা আলাদা, উৎস আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা এবং লোকাচারও আলাদা। সেই দেশে এক ভাষার মানুষের অন্য ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সামান্য হলেও জানার আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। কারণ এই ভাষাগুলির অনেকগুলিই আজ বিপন্ন। যেমন ওডিশা অঞ্চলে প্রায় বিপন্ন ও হারিয়ে যাওয়া একটি ভাষা রয়েছে, নাম গোরুম। এতে কথা বলেন ২০ জন। অথচ ৯৪৪৫ জন মানুষ আছেন তাঁদের মাতৃভাষা এই গোরুম। এটি মুন্ডা ভাষার অংশ। অন্ধ্র প্রদেশেও এই ভাষার চল ছিল। ভাষাবিদদের আশঙ্কা, একটি ভাষা হারিয়ে যাওয়া ও পৃথিবী থেকে একটি প্রাণীর কোনও প্রজাতি হারিয়ে যাওয়ার বিপদ সমান সমান। কাজেই লুপ্তপ্রায় ভাষার প্রয়োগ ও চর্চার বিকাশ প্রয়োজন।
তার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ভাষা নীতি যা আজও গৃহীত হয়নি। এ দেশের ৮৮ শতাংশ মানুষ মাত্র একটি ভাষা জানেন। ভাষা নিয়ে এদেশে রক্তপাতও কম হয়নি। উগ্রতার তীব্র বহিঃপ্রকাশও রয়েছে। এক বিপণন কর্মীর অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। তিনি পদমর্যাদায় একটি ওষুধ কোম্পানির উচ্চপদস্থ আধিকারিক, গিয়েছেন আসামে। বাড়ি ত্রিপুরায়। কাজ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়। পদোন্নতির পর উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি তার এলাকাভুক্ত হয়েছে। প্রথমদিন গুয়াহাটিতে গিয়ে এক প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গী অধঃস্তন কর্মীকে নিয়ে গিয়েছেন। প্রাথমিক পরিচয় ইংরেজিতে হওয়ার পর ওই আসামভাষী ডাক্তার প্রশ্ন করেছেন অসমীয়া জানেন কী না? জবাব নেতিবাচক। তখন তিনি ওই ব্যক্তিকে তেমন গুরুত্ব দিতে চাননি। এটা হয়তো একটা উদাহরণ মাত্র। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আসামবাসীদের বিচার করা ঠিক হবে না। তবে এই ধরনের কমবেশি তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেই।
বাঙালীরা আজকাল বিশেষত নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ইংরাজী-হিন্দিতে কথা বলতেই বেশি পছন্দ করেন। এর কারণ অবশ্যই সর্বভারতীয় শিক্ষা পর্ষদগুলিতে পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। এমনিতেও বাঙালীরা সর্বভারতীয় স্তরে ইংরেজিতে ভাব বিনিময় করতেই বেশি পছন্দ করে। আবার বাঙালীর হিন্দি বলা নিয়েও নান হাসিমস্করা চালু আছে। হিন্দি সিরিয়াল অথবা আগেরদিনে সিনেমাতেও একজন বাংলাভাষী চরিত্র রাখা হতো স্রেফ কমিক রোল হিসাবে। আবার একতাও ঠিক, অন্যভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাঙালীদেদের আগ্রহ তো সামাজিক বাধ্যবাধকতার গণ্ডি অতিক্রম করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চেহারা নেয়। কিন্তু সারা দেশের চেহারাটা একটু অন্যরকম। যাঁকে সাধারণ অর্থে সঙ্কীর্ণতা বলা হয় দেশের নানা প্রান্তে তাই কিন্তু আত্মমর্যাদা নিজ রাজ্যের ও সম্প্রদায়ের গরিমা সংরক্ষণের স্তরে পৌঁছে আছে।
অতএব? সাধারণত অতএব মানে সিদ্ধান্তের স্তর। অথচ ভাষা নিয়ে জটিলতায় অতএব এর পরে প্রশ্ন চিহ্ন। ইংরেজি মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি? ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন? মাতৃভাষায় শিক্ষাকে প্রাধান্য? একটা গোলকধাঁধা, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ভাষাসঙ্গম নামে একটি কর্মসূচি নিয়েছে। তাতে ২২টি ভাষায় ৫টি বাক্য—নমস্কার, তোমার নাম কি? আমার নাম— কেমন আছো? আর ভালো আছি। এই পাঁচটি বাক্য বিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত শেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কার্যকারিতা কতদূর তা প্রশ্নের অতীত নয়। তবে ভাষা নিয়ে বহুভাষিক এই দেশে সংশয় কাটছে না। ইতিমধ্যেই আরও একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আসন্ন। ‘ইস্কুলে কেন বাংলাটা পড়ায় না ইংলিশে’ জাতীয় কবিতা কিংবা ‘মোদের গরব মোদের আশা’ গানের মহড়া চলছে পুরোদমে। ‘প্রশ্ন—একদিন এই বর্ণাঢ্য আবেগ আর বাকি ৩৬৪ দিন একটি অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ও জলন্ত প্রশ্ন নিয়ে উদাসীনতা দু’টোর ভারসাম্য কীভাবে হবে? ভারসাম্য তো পড়তেই হবে।
তাই শুরু হোক একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণ—তৈরি হোক জনতার ভাষানীতি যা হোক সর্বজনগ্রাহ্য।
কলকাতা থেকে কৃশাণু ভট্টাচার্য