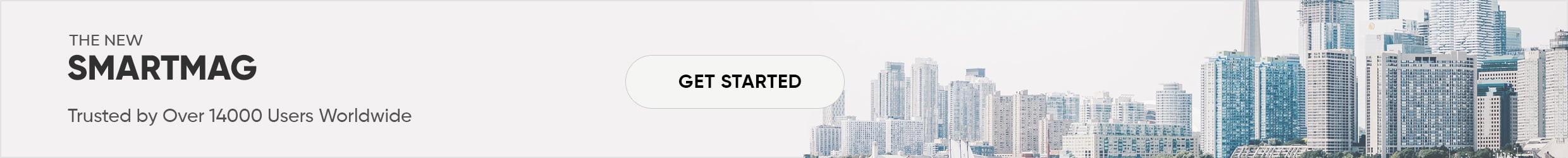বাংলাদেশের সংগীতাঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র শবনম মুশতারী একদিন কাউকে চিনতে পারছিলেন না। পরে জানা গেল, তিনি ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। একই রোগে ভুগছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ও সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সহধর্মিণীও। এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা আক্ষেপ করে বলেন, “আমাকে ছাড়া সে আর কাউকেই চেনে না। আমি চলে গেলে তার কী হবে!”
এই উদাহরণগুলো আধুনিক চিকিৎসার নাগালের মধ্যে থাকা মানুষের। অথচ বাস্তবতা হলো—ডিমেনশিয়া আজ সব শ্রেণি-পেশার প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য এক ভয়ঙ্কর হুমকি।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রায় ৫৭ মিলিয়ন মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে বাস করেন। বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮ শতাংশ, অর্থাৎ প্রতি ১২ জনে একজন ডিমেনশিয়ায় ভুগছেন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিমেনশিয়া বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী মৃত্যুর ৭ম প্রধান কারণ।
ডিমেনশিয়া সম্পর্কে এখনো সমাজে রয়েছে নানা ভুল ধারণা। অনেকেই একে উন্মাদনা বা মতিভ্রম হিসেবে মনে করেন। কেউবা অতীন্দ্রিয় শক্তির ছায়া কিংবা পাপের ফল বলেও বিশ্বাস করেন। এ কারণে পরিবারগুলো বিষয়টি গোপন রাখতে চান। এতে চিকিৎসা ও যত্নে বিলম্ব ঘটে, ফলে রোগীর অবস্থা দ্রুত অবনতি ঘটে এবং পরিবার এক অসহনীয় সংকটে পড়ে।
২০১৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান জানিয়েছিল, ২০২৫ সালের মধ্যে অন্তত ৭৫ শতাংশ দেশকে ডিমেনশিয়া প্রতিরোধ ও যত্ন সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ২৫ শতাংশ দেশ তা করতে পেরেছে।
বাংলাদেশে প্রবীণ নীতিমালা, মানসিক স্বাস্থ্য আইন ও ভরণপোষণ আইন থাকলেও ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সুরক্ষা নেই। এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তেও এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই।
বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত অনেক ধনী প্রবীণও সন্তানের অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার হন। প্রচলিত আইনে স্পষ্ট নেই—সন্তানের অবহেলা বা নির্যাতনের কারণে কোনো পিতার মৃত্যু হলে সেই সন্তান উত্তরাধিকারী হবেন কি না।আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যয় ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা কীভাবে হবে।
ফলে পরিবারে দায় চাপানোর প্রবণতা দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত একজন সন্তানকেই পুরো দায়িত্ব নিতে হয়।
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ডিমেনশিয়া মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন:
জাতীয় পর্যায়ে ডিমেনশিয়া প্রতিরোধ ও যত্ন নীতিমালা প্রণয়ন।
ভরণপোষণ ও উত্তরাধিকার বিষয়ে আইনে স্পষ্ট ধারা সংযোজন।
ডিমেনশিয়া আক্রান্তদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থিক সহায়তা চালু।
জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে ভ্রান্ত ধারণা ও কলঙ্ক দূর করা।
সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বিশেষ যত্নকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচর্যাকারী প্রশিক্ষণ।
বিশেষজ্ঞরা বলেন, ডিমেনশিয়া শুধু একজন ব্যক্তিকে নয়, পুরো পরিবারকে ভেঙে দেয়। এ রোগে আক্রান্তরা একসময় তাদের শ্রম, মেধা ও শক্তি সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ব্যয় করেছেন। এখন রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব তাদের শেষ দিনগুলোকে মর্যাদাপূর্ণ, নিরাপদ ও আরামদায়ক করে তোলা।
“ডিমেনশিয়া আক্রান্ত প্রবীণদের সামাজিক ও আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা না গেলে, এটি শুধু চিকিৎসাগত নয়, এক বড় মানবিক ব্যর্থতা হয়ে দাঁড়াবে।” —জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত
সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি