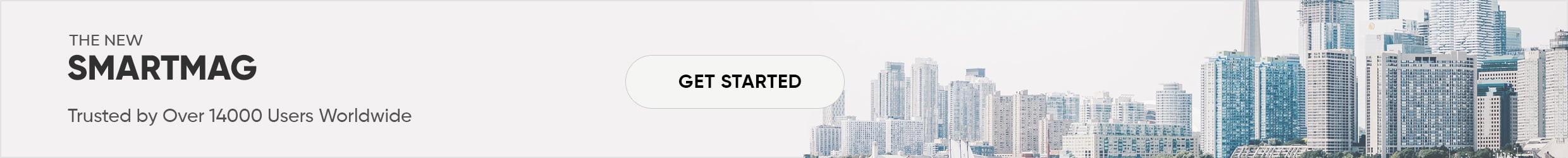বর্ষা যায় শরৎ আসে। প্রকৃতির নিয়মে ঋতু বদলায়। গাছেরাও বদলায়। যে বেরিয়াগাছে বর্ষাকালে থোকা ধরে ফুল ফুটতে দেখেছিলাম, সেসব ফুল এখন শরতে এসে ফলে পরিণত হয়েছে।
শরতের এক মেঘলা সকালে ধানমন্ডি ঝিলের পশ্চিম পাড়ের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল বেরিয়ার সেসব ফল। গাছ দুটি এত উঁচু যে কাছ থেকে ফলের দেখা পাওয়ার উপায় নেই। উঁচু ডালপালার মাথায় থোকা ধরে ঝুলছে ফলগুলো। থোকা ধরা সেসব সবুজ ফল দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, সবুজরঙা হাইড্রেঞ্জিয়া ফুল।
এরূপ থোকা ধরা সবুজ রঙের হাইড্রেঞ্জিয়া ফুলের দেখা পেয়েছিলাম আমেরিকায় নায়াগ্রা জলপ্রপাতের পার্কে। বেরিয়ার পাতাগুলোর আকার-আকৃতিও তো সেসব হাইড্রেঞ্জিয়া পাতার মতো। তফাতটা হলো হাইড্রেঞ্জিয়া বীরুৎ বা গুল্ম শ্রেণির গাছ আর বেরিয়া বৃহৎ বৃক্ষ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসির সামনে বুদ্ধ নারকেলগাছের পাশে মানিকজোড়ের মতো একটি প্রাচীন বেরিয়াগাছ তার প্রাচীনত্বের সাক্ষী দিচ্ছে। নিসর্গী দ্বিজেন শর্মাও ১৯৬৫ সালে সে গাছের দেখা পেয়েছিলেন সেখানে, সে গাছ সম্পর্কে তিনি তাঁর শ্যামলী নিসর্গ বইয়ে বিস্তারিত লিখেছেন বেশ রসিয়ে রসিয়ে। তাঁর অনুমান, যিনি এ গাছ দুটি সেখানে লাগিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন রসিক প্রকৃতিপ্রেমী ছিলেন। সেই প্রকৃতিপ্রেমী ছিলেন সম্ভবত রমনার বৃক্ষরোপণবিদ আর এল প্রাউডলক। তিনি বেরিয়া ও বুদ্ধ নারকেলগাছ মিয়ানমার থেকে এনে ঢাকা শহরে পথতরু হিসেবে লাগিয়েছিলেন। এ দুটি গাছের পাতার চেহারায় আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে। ফুল-ফল না দেখে শুধু পাতা আর গাছ থেকে এ দুটি গাছকে সহজে আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায় না। বুদ্ধ নারকেল জংলি বাদামগাছের স্বগোত্রীয় আর বেরিয়া পাটগাছের স্বগোত্রীয়—দুটি গাছের প্রজাতি ও গোত্র সম্পূর্ণ আলাদা। বেরিয়ার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম Berria cordifolia এবং গোত্র টিলিয়েসি।
দ্বিজেন শর্মা বেরিয়ার কোনো বাংলা নাম খুঁজে পাননি। বাংলাদেশের উদ্ভিদ নামকরণের অভিধান বইটিতে খুঁজতে খুঁজতে শেষে বেরিয়ার একটি বাংলা নাম পেয়ে যাই, চাবানদালাই। বেরিয়া নামটি জনৈক চিকিৎসক এনড্রু বেরিয়ার নামের স্মারক। বেরিয়া এই গাছের জেনাস বা গণগত নাম, ইংরেজি নাম Trincomali wood। বেরিয়াগাছ প্রায় ২০ মিটার লম্বা হয়। পানপাতার মতো পাতা, বড়, থোকা ধরে সাদাটে গোলাপি ফুল ফোটে গ্রীষ্ম-বর্ষায়। ফুল খুব ছোট হলেও তার শাখায়িত মঞ্জরির অজস্র প্রস্ফুরণ গাছকে শোভাময় করে তোলে। সাদা পাপড়ির সঙ্গে সোনালি হলুদ পরাগচক্র এ ফুলের আসল সৌন্দর্য। ফলের সঙ্গে বৃতিগুলো স্থায়ীভাবে লেগে থাকে। ঘন বাদামি ও ফুলের মতো সেগুলোও থাকে অজস্র। ছোট্ট গোলাকৃতির শক্ত কাঠের মতো ফলের চারদিকে বিক্ষিপ্ত পাপড়ির মতো ছয়টি শুকনা পাখনা বা ডানা থাকে।
বেরিয়াগাছ মূলত আসবাব তৈরির কাঠের জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রাচীনকালে জাহাজ নির্মাণের জন্য এ গাছের কাঠের কদর ছিল। কেননা বেরিয়াগাছের গুঁড়ি সরল, লম্বা, উন্নত, ধূসর, মসৃণ ও মজবুত। এ গাছের গোড়া থেকে অনেকটা উঁচু পর্যন্তÍকোনো শাখা বা ডালপালা থাকে না। চারা বাড়ে ধীরগতিতে, কিন্তু একবার বড় হয়ে উঠলে তখন গাছ দ্রুত বাড়ে। বীজ ও শিকড় থেকে বের হওয়া চারা (সাকার) দিয়ে বংশবৃদ্ধি করা যায়। বেরিয়ার বীজগুলো বেশ যন্ত্রণাদায়ক। কেননা বীজের গায়ে শক্ত যে শুঁয়ো থাকে, হাত দিয়ে ধরলে বা গায়ে লাগলে সেগুলো ত্বকে ফুটে যন্ত্রণা দেয়।
বুদ্ধ নারকেলগাছের ফল বড় ও শক্ত কাঠের মতো খোলাযুক্ত এবং বেরিয়ার ফল ছোট ও ডানাওয়ালা। একটা ফলকে খুব কাছ থেকে নিবিড়ভাবে দেখার চেষ্টা করলাম, কোথায় তার ডানা? সত্যিই তো, খাটো বোঁটার ওপর একটা ছোট্ট গুটির মতো ফল, সেই ফলের তিন দিক থেকে পাখির ডানার মতো তিন জোড়া চ্যাপটা ডানা। ডানাগুলোর গড়নটা বেশ অদ্ভুত, খানিকটা পাতার মতো শিরাযুক্ত, অগ্রভাগ সরু ও সুচালো, মাঝখানটা চওড়া।
গাছ বেশ কষ্ট সইতে পারে। তবে এ গাছ জলাবদ্ধতা সইতে পারলেও খরা সইতে পারে না। অনুর্বর মাটিতে জন্মাতেও তার আপত্তি নেই। যত্নœনা নিলেও অরণ্যবৃক্ষের মতো অনাদরে বাড়ে। দক্ষিণ এশিয়া বেরিয়ার জন্মস্থান। আফ্রিকাতেও এখন এ গাছ আছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিসমাস দ্বীপের অরণ্যে এ গাছ দেখা যায়। তবে বাংলাদেশে এটি দুষ্প্রাপ্য, সারা দেশে বেরিয়াগাছ আছে হাতে গোনা কয়েকটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির চত্বর ছাড়া বর্তমানে ধানমন্ডি ১২/এ নম্বর রোডের ৮৩ ও ৮৭ নম্বর বাড়ির সামনে ফুটপাতের ওপর তিনটি বেরিয়াগাছ ওদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।
বেরিয়াগাছের চারা তৈরি ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।