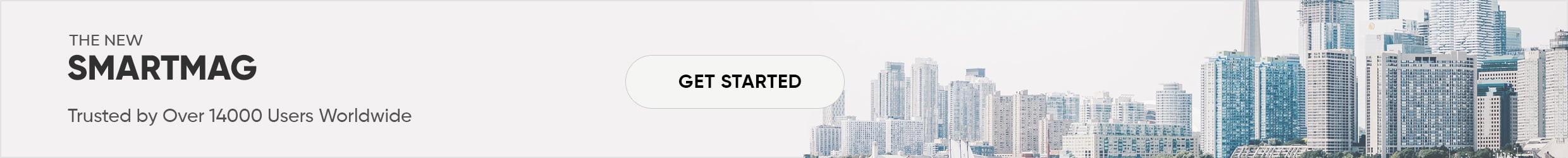বেশ কিছুদিন ধরে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। একটি দেশের সামগ্রিক রাজনীতিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন যে প্রধান সংবাদ শিরোনাম হতে পারে, এটি অবাক করার মতো ব্যাপার। ডাকসুর ভোটার সংখ্যা একটি ওয়ার্ডের চেয়েও অনেক কম। তারপরও এটি নজর কেড়েছে।
নির্বাচন হলো মঙ্গলবার। শুনেছি, অনেকেই টেনশনে রাতে ঘুমাতে পারেননি। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে ফলাফল জানতে পেরেছি। যেহেতু এই নির্বাচন নিয়ে আমার মধ্যে কোনো ‘অবসেশন’ ছিল না, তাই আর দশটা খবরের মতো এটাও স্বাভাবিক মনে হয়েছে।
সকালে আমি হাঁটাহাঁটি করি। তো সেখানে পরিচিতদের সঙ্গে আড্ডা আর চা খাওয়া হয়। আজ সেখানে আড্ডার মূল বিষয় ছিল ডাকসু নির্বাচন। কিছু মানুষ এটাকে সহজভাবেই নিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, এ রকমই তো হওয়ার কথা। আবার অনেকেই এটিকে হজম করতে পারছেন না। বলছেন, এটি কী ঘটে গেল!
আমি ১৯৭০ সাল থেকে ডাকসু নির্বাচন দেখে আসছি। আমি দেখেছি, ডাকসুতে কখনোই সরকারের লেজুড় সংগঠন জেতেনি। তার মানে এই নয় যে সরকারি দল নির্বাচন ম্যানিপুলেট করতে চায়নি।
ডাকসুতে সরাসরি ভোটে প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালে। সেবার ছিল ছাত্রলীগের জয়জয়কার। ’৭২ সালে ছাত্রলীগ দুই ভাগ হলো। সেই ফাঁকে মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন জিতে গেল। ১৯৭৩ সালে চালচিত্র গেল পাল্টে। ছাত্রদের সবচেয়ে লড়াকু আর মেধাবী অংশটি জাসদ-সমর্থিত মুজিববিরোধী ছাত্রলীগের ব্যানারে ডাকসুতে প্যানেল দিল। তাদের ঠেকাতে মুজিববাদী ছাত্রলীগ আর মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন দিল যৌথ প্যানেল।
সন্ধ্যায় ভোট গণনার সময় যখন দেখা গেল জাসদ ছাত্রলীগের জয়রথ এগিয়ে যাচ্ছে, তখন মুজিববাদী যৌথ বাহিনীর সশস্ত্র গুন্ডাদের হস্তক্ষেপে ভোট গণনা ভন্ডুল হয়ে যায়। এ করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তারা কয়েকটি হলের প্রতিপক্ষ দলের সদস্য বা সমর্থকদের কামরায় হামলা চালায়, লুটপাট করে। ওই রাতে মুহসীন হলের ৩১১ নম্বর কামরার তালা ভেঙে ওরা আমার সবকিছু লুটে নিয়েছিল।
যাঁরা ডাকসু নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের জন্ম একাত্তরের অনেক পরে। তাঁরা একাত্তর দেখেননি, পঁচাত্তর দেখেননি, নব্বই দেখেননি। তাঁরা দেখেছেন শেখ হাসিনার শাসন আর খালেদা জিয়ার বিরোধিতা। এখান থেকেই তরুণদের মধ্যে একধরনের মন তৈরি হয়ে থাকতে পারে যে তাঁরা প্রচলিত ধারার রাজনীতি আর রাজনীতির বিরোধিতাকে সমর্থন করেন না; কিন্তু তাই বলে ছাত্রশিবির? একাত্তরের প্রজন্মের কাছে এটি একটি বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।
সরকারের চিন্তাটা ছিল এ রকম—একটি ভিন্নমতের সংগঠন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জিতে যাবে, এটি হজম করার মতো মানসিকতা সরকারি দল ও তার সহযোগীদের ছিল না। উপাচার্য ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর মধ্যে কোনো মনস্তাপ ছিল না। এরপর তাঁর প্রমোশন হলো। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন। তারপর হলেন মন্ত্রী।
এরপর আমরা দেখলাম, দলীয় সরকারের অধীন জিয়া-এরশাদ জমানায় যতবার ডাকসু নির্বাচন হয়েছে, কোনোবারই সরকারি দলের অঙ্গসংগঠন জয় পায়নি। একপর্যায়ে গণতন্ত্রের দুই মানসকন্যা গদিনশিন হয়ে ডাকসু নির্বাচনই হতে দেননি। এখানে একটা সরল উপসংহার টানা যায়। তরুণেরা হচ্ছেন এস্টাবলিশমেন্টবিরোধী। সারা দুনিয়ায় এই প্রবণতা। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। গুন্ডামি করে নির্বাচনে জেতা যায় না বলেই সরকারগুলো নিয়মিত নির্বাচন হতে দেয়নি।
অনেক বছর পর একটি মুক্ত পরিবেশে এ বছর ডাকসু নির্বাচন হলো। কিছু কিছু সমালোচনা হয়েছে। কেউ কেউ ‘প্রত্যাখ্যান করলাম’ জাতীয় আওয়াজ দিচ্ছেন। হেরে গেলে এ রকম রব ওঠে। সূক্ষ্ম কারচুপি, স্থূল কারচুপি, পুকুরচুরি, সাগরচুরি—এই জাতীয় কথার সঙ্গে আমরা কমবেশি পরিচিত। ১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত আমরা এসব শুনেছি।
এবার ডাকসুতে বড় জয় পেয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির। এটি জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সংগঠন। জামায়াত-শিবির সম্পর্কে জনমনস্তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এরা পাকিস্তানপন্থী, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। এ কথাটি কারা বলছেন? বলছেন তাঁরাই, যাঁরা একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ন্যায়যুদ্ধ মনে করেন।
কথা হলো, যাঁরা ডাকসু নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের জন্ম একাত্তরের অনেক পরে। তাঁরা একাত্তর দেখেননি, পঁচাত্তর দেখেননি, নব্বই দেখেননি। তাঁরা দেখেছেন শেখ হাসিনার শাসন আর খালেদা জিয়ার বিরোধিতা। এখান থেকেই তরুণদের মধ্যে একধরনের মন তৈরি হয়ে থাকতে পারে যে তাঁরা প্রচলিত ধারার রাজনীতি আর রাজনীতির বিরোধিতাকে সমর্থন করেন না; কিন্তু তাই বলে ছাত্রশিবির? একাত্তরের প্রজন্মের কাছে এটি একটি বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।
এ দেশে রাজনৈতিক প্রপাগান্ডিস্টরা যা-ই প্রচার করুক না কেন, আমরা জানি, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বড় দুটি দল হলো আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। তৃণমূল পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি। বাকি দলগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা কাগুজে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে সমর্থন করতে গিয়ে জামায়াতে ইসলামী জনবিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গিয়েছিল অস্তাচলে। তাদের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের অস্তিত্ব ছিল না।
অবাক করার বিষয় হলো, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার কারণে এ দেশে কোনো দল নিষিদ্ধ হয়নি। নিষিদ্ধ হয়েছিল রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার। ১৯৭৩ সাল থেকেই বাংলাদেশে আগের মতোই রাজনীতিতে ধর্মীয় জিগির শুরু হয়। পঁচাত্তরে এসে এটি আরও বেগবান হয়। সত্তর দশকের শেষের দিকে জামায়াতে ইসলামীর পুনরুত্থান ঘটে। এরশাদের জমানায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত আর বাম দলগুলো যুগপৎ আন্দোলন করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচনের দাবি প্রথম করেছিল জামায়াত। সেই দাবি সবাই লুফে নেয়।
১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী রেসে অংশ নিয়ে জামায়াত প্রথমবারের মতো নিজস্ব প্রতীক নিয়ে ১০টি আসনে জয় পেয়ে সংসদে যায়। ফলে দলটি রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বৈধতা পেয়ে যায়। জামায়াতের সদস্যরা শেখ হাসিনাকে নেতা মেনে সংসদে বিরোধী দলের বেঞ্চে বসেন। এভাবে আওয়ামী লীগের হাত ধরে জামায়াতের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার শুরু।
১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে সমঝোতা করে জামায়াত পায় ১৭টি আসন। তাদের লিখিত সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করে। পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে জামায়াত বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আন্দোলন গড়ে তোলে। ২০০১ সালে বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে জামায়াত নির্বাচন করে সরকারের অংশ হয়। সেই সঙ্গে সমাপ্ত হয় দলটির পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া। ২০২৫ সালে এসে জামায়াতের একাত্তরের ভূমিকা নিয়ে জনগণের মধ্যে অভিযোগ ও ক্ষোভ থাকলেও তাদের বিরোধিতা করার নৈতিক অবস্থান আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেই।
পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের উত্তরসূরি ইসলামী ছাত্রশিবির আশির দশক থেকেই নিজেদের সংগঠিত করছে। এর আগে ঢাকার বাইরে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতি তারা নিয়ন্ত্রণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারই তারা প্রথম চালকের আসনে বসে গেল। কেন এমন হলো—এই প্রশ্ন করা যেতে পারে তরুণ ভোটারদের। সত্তরোর্ধ্ব অবসরপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের একাত্তরের ঘেরাটোপে আটকে থাকা চিন্তার প্রভাব যে তরুণদের মধ্যে ক্রমে বিলীয়মান, এটা তাঁরা অনেকেই বুঝতে চাইছেন না।
জাতীয় নির্বাচন হবে পাঁচ মাস পর। ডাকসু নির্বাচনকে জাতীয় নির্বাচনের রিহার্সাল হিসেবে দেখেন কেউ কেউ। এ মাসে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে। ডাকসু নির্বাচনের প্রভাব সেগুলোতে কতটুকু পড়বে, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যদি একটি প্যাটার্ন বা প্রবণতা বেরিয়ে আসে, তা জাতীয় নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে।
জাতীয় নির্বাচনে অনেক উপকরণ ও অনুষঙ্গ কাজ করে। সেখানে সংগঠনের বিস্তৃতি, অর্থ, প্রচারের পেশাদারত্ব, জনপ্রিয় প্রার্থী খুঁজে পাওয়া, প্রার্থীর ব্যক্তিগত আচরণ ও অতীত, দলগুলোর আন্তসম্পর্ক ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভেতরে বা বাইরে থেকে যদি কোনো ধরনের নাশকতা না হয়, যদি সত্যিকার নিরপেক্ষ সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হয়, তাহলে তার ফলাফল কেমন হবে, তা নিয়ে মন্তব্য করার সময় এখনো আসেনি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আমরা দেখেছিলাম, পূর্বাভাস কত ভুল হতে পারে।
এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। ভোটারদের মধ্যে বেশির ভাগই তরুণ। কে অতীতে কী করেছেন, তা নিয়ে জাবর কেটে তাঁদের জীবন চলবে না। তাঁরা কী চান, রাজনৈতিক দলগুলোকে সেটি বিবেচনায় নিতে হবে। ‘কাল্ট ওরশিপ’ বা ব্যক্তিপূজার বড়শি দিয়ে তরুণ মন গেঁথে ফেলার দিন সম্ভবত শেষ।