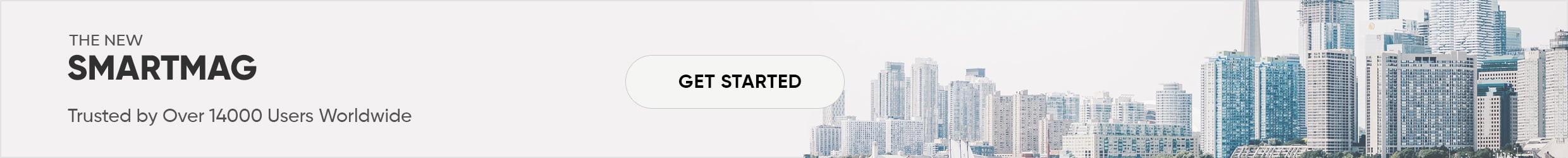বিশ্ববাণিজ্য দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এটি পণ্য, সেবা ও সম্পদের বাণিজ্য সহজতর করে, যার মাধ্যমে দেশগুলো তাদের তুলনামূলক সুবিধা অনুসারে উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে পারে, যেখানে উৎপাদন খরচ কম হয়। এর ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার হয় এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। প্রাচীন সিল্ক রোড থেকে আধুনিক বহুপক্ষীয় বাণিজ্যব্যবস্থায়, বৈশ্বিক বাণিজ্য শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেনি; বরং সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং কূটনৈতিক সম্পর্ককেও শক্তিশালী করেছে।
কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববাণিজ্যব্যবস্থা বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ২০২৫ সালের এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ’ নামে দেশভিত্তিক একটি পাল্টা শুল্কনীতি ঘোষণা করেন। এই নীতির মূল লক্ষ্য ছিল দেশটির দেশীয় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা, বাণিজ্যঘাটতি কমানো এবং ‘অন্যায্য বিদেশি বাণিজ্য অনুশীলন’ প্রতিরোধ করা। নীতির আওতায় সব ধরনের আমদানির ওপর ১০ শতাংশ হারে সর্বজনীন শুল্ক আরোপ করা হয়। পাশাপাশি যেসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে, তাদের জন্য আলাদা করে বাড়তি শুল্ক ধার্য করা হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও বাংলাদেশ এই শুল্কবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় রয়েছে। নতুন হার যদিও এপ্রিল মাসে প্রস্তাবিত ৩৭ শতাংশ থেকে কম, তবু ভিয়েতনাম যেভাবে আলোচনার মাধ্যমে ২০ শতাংশ শুল্ক নিশ্চিত করেছে, তার তুলনায় এটি অনেক বেশি। ভারত ও পাকিস্তানের শুল্কহার এখনো চূড়ান্ত না হলেও ভিয়েতনাম, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার ওপর আরোপিত শুল্ক দেখেই বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা উদ্বিগ্ন। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, মার্কিন বাজারে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়বে।
নতুন এই শুল্কগুলো আগের শুল্কের ওপর অতিরিক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশনের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের রপ্তানিপণ্যের গড় শুল্ক ছিল প্রায় ১৫ শতাংশ। এতে নতুন ৩৫ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হলে মোট কার্যকর শুল্ক দাঁড়ায় প্রায় ৫০ শতাংশ, যা বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের দাম ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে কমিয়ে দিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ‘রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ’ নীতির ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত (আরএমজি) সবচেয়ে বেশি চাপের মুখে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি মাত্র শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ৬ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার হলেও দেশটিকে ৩৫ শতাংশ শুল্কের আওতায় আনা হয়েছে, যা ১৪টি লক্ষ্যভুক্ত দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। অথচ আরএমজি খাত বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি এবং প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক, যাঁদের অধিকাংশ নারী, এই খাতের ওপর নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় একক রপ্তানি বাজার, যেখানে প্রতিবছর প্রায় আট বিলিয়ন ডলারের পোশাক যায়।
আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পোশাকে গড় শুল্ক ছিল ১৫ শতাংশ। এখন নতুন ৩৫ শতাংশ যুক্ত হওয়ায় মোট কার্যকর শুল্ক দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সবচেয়ে বড় শঙ্কার বিষয় হলো, বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২০ শতাংশ শুল্কে সমঝোতা করেছে, যা বাংলাদেশের তুলনায় ১৫ শতাংশ কম। ইন্দোনেশিয়াও প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ হিসেবে তুলনামূলকভাবে কম শুল্কের সুবিধা পাচ্ছে। এর ফলে মার্কিন ক্রেতারা ভিয়েতনাম, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান বা কেনিয়ার মতো দেশ থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে পোশাক আমদানির দিকে ঝুঁকছেন।
বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) মতে, এই শুল্কবৃদ্ধির কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্ডার (কার্যাদেশ) ১৫-২০ শতাংশ কমে যেতে পারে। এর ফলে শুধু রপ্তানি আয় নয়, কাঁচামাল, প্যাকেজিং, পরিবহন ও ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট অনেক খাতও প্রভাবিত হবে এবং কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতি কোনো বৈশ্বিক নিয়ম বা ন্যায্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং রাজনৈতিক ও কৌশলগত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তৈরি। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও দুর্বল অর্থনীতির ওপর এ ধরনের বৈষম্যমূলক শুল্ক আরোপ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ‘ন্যায্য ও সমান সুযোগভিত্তিক’ বাণিজ্যনীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন। তৈরি পোশাকশিল্পে এই চাপ একটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সূচনা করেছে, যা দেশীয় সরবরাহ শৃঙ্খলা ও আর্থিক খাতেও প্রতিফলিত হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কবৃদ্ধির এই ধাক্কা কেবল তৈরি পোশাকশিল্পেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এর ঢেউ পুরো রপ্তানি খাত এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর ছড়িয়ে পড়তে পারে। তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি, যা বহু সহায়ক শিল্প ও সেবা খাতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এই খাতে অর্ডার কমে গেলে তার প্রভাব পড়ে পুরো সরবরাহ ও সাপোর্ট সেক্টরে।
শুল্কবৃদ্ধির ফলে যদি যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্ডার কমে যায়, তাহলে প্রথম ধাক্কাটি লাগবে কাপড়, সুতা, বোতাম, জিপারসহ বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহকারীদের ওপর। পাশাপাশি প্যাকেজিং খাত, যেমন কার্টন, লেবেল, পলিব্যাগ প্রস্তুতকারক, তাদেরও উৎপাদন ও বিক্রি কমে যাবে। রপ্তানির পরিমাণ কমে গেলে পরিবহন খাতেও স্থবিরতা দেখা দেবে, কম মালামাল পরিবহনের কারণে ট্রাক, কনটেইনার ও জাহাজ কম ব্যবহৃত হবে, যার ফলে বন্দর ও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপোতে অদক্ষতা তৈরি হতে পারে।
সব মিলিয়ে এটি একধরনের ‘চেইন রিঅ্যাকশন’ তৈরি করবে, যেখানে একটির প্রভাব অন্যটিতে ছড়িয়ে পড়বে এবং এই ধারা চলতে থাকলে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে বড় ধরনের সংকট দেখা দিতে পারে।
আর্থিক খাতেও এ প্রভাব গভীর হতে পারে। রপ্তানিনির্ভর ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলো যদি তারল্য–সংকটে পড়ে, তাহলে ব্যাংকঋণ পরিশোধে সমস্যা দেখা দেবে। এতে খেলাপি ঋণের হার বাড়বে, ব্যাংকগুলো ঝুঁকিতে পড়বে। একইভাবে বিমা খাতও বিপদে পড়বে। কার্গো পরিবহন কমে গেলে প্রিমিয়াম আদায় হ্রাস পাবে, অন্যদিকে দাবি (ক্লেইম) বেড়ে যেতে পারে।
সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হলো এই বহুমুখী ধাক্কা শ্রমবাজারেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি না হয়ে বরং কাজ হারানোর আশঙ্কা বাড়বে। এতে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বাড়বে, পরিবারে আয় কমবে এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা, হতাশা ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়বে, যা দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান চাপকে আরও জটিল করে তুলবে।
শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েন প্রশমনে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হয়েছে এবং কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই প্রক্রিয়ায় কৃষি, বিমান চলাচল ও জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা দেওয়ার কথা আলোচিত হচ্ছে, যদিও সরকারিভাবে বিষয়টি এখনো নিশ্চিত করা হয়নি।
এই কৌশলের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে ‘জিটুজি’ (সরকার থেকে সরকার) চুক্তির মাধ্যমে প্রায় তিন লাখ টন গম আমদানি করতে সম্মত হয়েছে বলে এমন খবর শোনা গেছে। এর সম্ভাব্য মূল্য ভারত, রাশিয়া বা ইউক্রেন থেকে আমদানি করা গমের তুলনায় প্রতি টনে ২০-২৫ মার্কিন ডলার বেশি হতে পারে। পাশাপাশি পরিবহন ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে বেশি। একইভাবে বোয়িং বিমান কেনা এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা, গ্যাস টারবাইন, সেমিকন্ডাক্টর ও চিকিৎসা সরঞ্জামের আমদানিতে শুল্ক সমন্বয়ের বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে।
সরকারের এই উদ্যোগগুলো সহযোগিতার ইতিবাচক বার্তা দিলেও অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও বাণিজ্যিক যুক্তির নিরিখে ভবিষ্যতে এসব সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক উত্থাপিত হতে পারে। তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল গম আমদানি করতে গিয়ে সরকার হয়তো ভর্তুকি দিতে বাধ্য হবে। এর ফলে বাজেট-ঘাটতি বাড়তে পারে কিংবা বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি আরও তীব্রতর রূপ নিতে পারে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা মানসম্মত হলেও তা ভারত, পাকিস্তান বা ব্রাজিলের তুলার তুলনায় ব্যয়বহুল, যা মূল্য সংবেদনশীল তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।
এ ধরনের সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যৌক্তিক বিবেচিত হতে পারে, যদি এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্ক কমিয়ে আনে বা অগ্রাধিকারভিত্তিক কোনো বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে শুল্কছাড়ের ব্যবস্থা করে। তবে পারস্পরিক সুবিধাভিত্তিক এমন কোনো কাঠামো অনুপস্থিত থাকায় একতরফা তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল আমদানিতে বাধ্য হওয়া বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অবনতি ঘটাতে পারে। বিশেষত, যদি এর ফলে বিদেশের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হ্রাসের ঝুঁকি তৈরি হয়, তাহলে তা বাণিজ্যিক ভারসাম্যে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব পদক্ষেপ তাৎক্ষণিক সুবিধা বয়ে আনতে পারে। তবে অর্থনৈতিক টেকসই উন্নয়ন এবং বহুপক্ষীয় বাণিজ্যনীতির মূলনীতির সঙ্গে এর সামঞ্জস্য ‘সন্দেহজনক’। জ্যাকব ভাইনের ‘কাস্টমস ইউনিয়ন থিওরি’ অনুসারে, বাণিজ্যের নতুন সুযোগ সৃষ্টি না করে শুধু বাণিজ্য-বিচ্যুতি ঘটালে জাতীয় সামগ্রিক কল্যাণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ডেভিড রিকার্ডোর ‘তুলনামূলক সুবিধার তত্ত্ব’ আমাদের শিক্ষা দেয় যে একটি দেশের উৎপাদন ও আমদানিনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং খরচ সাশ্রয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় রাখতে হবে। অর্থাৎ কোনো পণ্যের আমদানি বা উৎপাদনে দেশের তুলনামূলক সুবিধা ও কর্মক্ষমতা উপেক্ষা করলে অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা বেড়ে যায়, যা দীর্ঘ মেয়াদে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এই পদক্ষেপগুলোর পরোক্ষ প্রভাব রাজনীতিকরণ ও কৌশলগত চাপের দিকে ইঙ্গিত করে, যা শুল্ক ও অশুল্ক শর্তের মাধ্যমে আরও গভীরভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।
বাণিজ্য এখন আর শুধু অর্থনৈতিক লেনদেনের বিষয় নয়, এটি ক্রমেই রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ভারসাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ নীতির আওতায় বাংলাদেশকে উচ্চ শুল্কের আওতায় আনার বিষয়টি কারও কারও দৃষ্টিতে বাণিজ্যঘাটতি কমানোর একটি প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আবার অনেকের মতে, এটি বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানকে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একটি কৌশল।
প্রস্তাবিত বাণিজ্যকাঠামোতে কিছু অশুল্ক শর্তও যুক্ত হতে পারে বলে কেউ কেউ ধারণা করছেন। এর মধ্যে রয়েছে—
নিষেধাজ্ঞা সামঞ্জস্য: যুক্তরাষ্ট্র যেসব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য নিষিদ্ধ করেছে, (যেমন রাশিয়া, ইরান), সেসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য স্থগিত রাখার শর্ত।
শুল্ক সামঞ্জস্য: তৃতীয় কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক বাড়ালে, বাংলাদেশেরও সমান হারে শুল্ক আরোপের বাধ্যবাধকতা।
অগ্রাধিকার সীমাবদ্ধতা: যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অন্য কোনো দেশকে বেশি বাণিজ্য–সুবিধা না দেওয়ার সম্ভাব্য শর্ত।
যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতির ফলে বাংলাদেশ কেবল দ্বিপক্ষীয় চাপ নয়, বরং বৈশ্বিক বাণিজ্য নিয়ে রাজনীতির অনিশ্চয়তা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। এই নীতি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নেতৃত্বাধীন নিয়মভিত্তিক বাণিজ্যকাঠামোকেই দুর্বল করছে। বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থা দুর্বল হলে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রবেশের সুযোগ কমে যাবে এবং দর-কষাকষির ক্ষমতাও ক্ষীণ হয়ে পড়বে।
এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন একটি সুদূরপ্রসারী ও পরিষ্কার নীতিনির্ভর কৌশল, যা মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এ ক্ষেত্রে টিকফাকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নীতিগত সংলাপ জোরদার করতে হবে। একই সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল আমদানি এড়িয়ে বিকল্প বাজার খোঁজা, পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানো ও দ্বিপক্ষীয়-বহুপক্ষীয় ভারসাম্য বজায় রেখে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা ধরে রাখার দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।
সর্বোপরি বাংলাদেশকে একটি ন্যায্য ও অংশগ্রহণমূলক বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার পক্ষে সক্রিয় অবস্থান নিতে হবে, যাতে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবিলায় শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়।
গোলাম রসুল অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা
মতামত লেখকের নিজস্ব