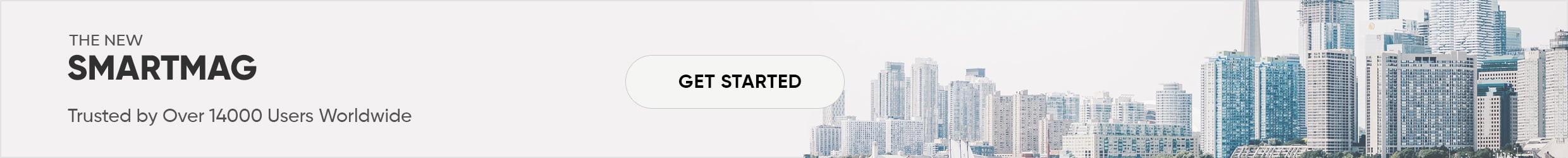সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে জেনেভা ও লন্ডনে যে বাণিজ্য আলোচনা হয়েছে, তা সাময়িক স্বস্তি দিলেও দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংকটের সমাধান দেয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এসব অস্থায়ী ব্যবস্থাকে ‘চুক্তি’ হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং দাবি করেছেন, এসব চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভালো।
কিন্তু চীন বিষয়টিকে একেবারেই ভিন্নভাবে দেখছে। চীনের মতে, তারা এ বাণিজ্য সংঘাত আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবং আরও আত্মনির্ভর হয়ে পার হয়ে এসেছে। চীন মনে করছে, তাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ভালো ফল দিচ্ছে।
২০১৮ সালে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এ কঠিন বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়। এর পর থেকে চীন এমন একটি কৌশল গ্রহণ করেছে, যেখানে প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক—দুই ধরনের পদক্ষেপ একত্রে রয়েছে।
আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে চীন তাদের বাণিজ্যপ্রবাহের পথ ঘুরিয়ে দিয়েছে; ডলারের ওপর নির্ভরশীল বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার বিকল্প খুঁজেছে এবং নিজেদের প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ অনেক গুণ বাড়িয়েছে।
ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদকেরা বিপাকে পড়েছেন এবং অতিরিক্ত দামে তাঁরা এসব উপকরণ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। এ বছরের এপ্রিলের শুরুতে চীন যখন বিরল খনিজের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শুরু করল, তখন তারা সহজেই বুঝতে পারল, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চাপ সৃষ্টি করার এক কার্যকর হাতিয়ার।
চীন অভ্যন্তরীণ বাজারে ভোগ বাড়াতে চেয়েছে। এটি তারা শুধু ভোক্তাপ্রবণতা বাড়ানোর জন্য করেনি, বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা গ্রিন টেকের মতো কৌশলগত খাতে চাহিদা বাড়ানোর জন্যও করেছে।
আক্রমণাত্মক কৌশল হিসেবে চীন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কঠোর করেছে এবং প্রতিপক্ষের ওপর দ্রুত ও সুচিন্তিতভাবে জবাব দেওয়ার সক্ষমতা দেখিয়েছে।
ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফার প্রশাসন যখন নতুন করে শুল্ক আরোপের হুমকি দেয় বা তা কার্যকর করে, চীন তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, কঠিন অবস্থান নিয়েছে এবং কখনোই ভয় পায়নি।
চীন শুধু প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না, বরং এই পুরো বাণিজ্য সংঘাতকে নিজেদের শর্তে পুনঃসংজ্ঞায়িত করছে।একই সময়ে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিগুলো আসলে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের শিল্প খাতের চীনের ওপর নির্ভরতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। বিশেষ করে বিরল খনিজ ও বিভিন্ন কাঁচামাল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে চীনের ওপর নির্ভরশীল, তা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে।
ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদকেরা বিপাকে পড়েছেন এবং অতিরিক্ত দামে তাঁরা এসব উপকরণ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। এ বছরের এপ্রিলের শুরুতে চীন যখন বিরল খনিজের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শুরু করল, তখন তারা সহজেই বুঝতে পারল, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চাপ সৃষ্টি করার এক কার্যকর হাতিয়ার।
ট্রাম্পের এ অনিয়মিত ও নাটকীয় শুল্ক নীতি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য একধরনের প্রচারণামূলক জয় এনে দিয়েছে। যদিও চীনের জনগণের কাছে ট্রাম্পকে প্রতিহত করা ততটা জনপ্রিয় কিছু নয়, তবুও এ যুদ্ধ তাদের একটি কৌশলগত সুবিধা দিয়েছে।
বৈশ্বিক দক্ষিণের (গ্লোবাল সাউথ) যেসব দেশ পশ্চিমা উন্নয়ন মডেলের প্রতি সন্দেহপ্রবণ, তারা এ সংকটে চীনের স্থিতিশীল অবস্থান দেখে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ‘বিশ্ব এক শতকে একবার দেখা যাওয়া বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে’ কথাটির ওপর আস্থা খুঁজে পাচ্ছে।চীন মনে করে, যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সংযোগ তৈরি হয়েছিল, তা ট্রাম্প প্রশাসন যেকোনো মূল্যে বিচ্ছিন্ন করতে চায় এবং এর মাধ্যমে ট্রাম্প চীনের উত্থান ঠেকিয়ে দিতে চান। চীন চায় না তাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধ হোক। চীন চায় না তাদের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা হোক। কিন্তু চীন মনে করে, চীন যদি বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়, তাহলে তারা সে বিচ্ছিন্নতাও মেনে নিতে পারবে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সামনে মাথা নত করবে না। চীন মনে করে, ট্রাম্প যে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করেছেন, সেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র হেরে যাবে।
এ কারণেই চীনা নেতৃত্ব, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা আত্মনির্ভরতা তৈরির দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা কমানো।
যদিও মার্কিন বাজারের চাহিদা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সঙ্গে তুলনা চলে না, তবুও চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ধরে নিচ্ছে, তারা আর যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না বা মার্কিন উচ্চ প্রযুক্তি পাবে না। সেটি মাথায় রেখেই তারা নিজেদের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে। চীনের প্রযুক্তি কোম্পানি হুয়াওয়ের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর দুর্দান্তভাবে কোম্পানিটির ঘুরে দাঁড়ানো এর একটি বড় উদাহরণ। এখন টিকটকের মালিক প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সও একই ধরনের চাপের মুখে রয়েছে। ট্রাম্প চান এটি মার্কিনদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হোক।
নিশ্চিতভাবেই ট্রাম্পের শুল্ক নীতির কারণে চীনের গায়েও আঘাত লেগেছে। বিশেষ করে কম দামের হালকা শিল্পপণ্য (যেমন পোশাক, জুতা) এসব খাতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে।
তবে এতে কিছু ইতিবাচক দিকও তৈরি হতে পারে। যেমন ছোট ছোট অদক্ষ প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে গিয়ে শিল্পে একধরনের সংহতি ও দক্ষতা বাড়বে। এতে বেকারত্ব বাড়তে পারে। কিন্তু চীনে যেহেতু অনেক কারখানাই অটোমেশনের মাধ্যমে চলে, সেহেতু এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ততটা গুরুতর হবে না।এর চেয়ে বড় কথা, চীন অতীতে এর চেয়ে বড় ধাক্কা সামলেছে। ১৯৯২ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বাজারভিত্তিক সংস্কারের কারণে ৭ কোটি ৬০ লাখ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছিলেন। সেটিও তারা সামাল দিয়েছে। সুতরাং আজকের কিছু ছাঁটাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা নড়বড়ে দেওয়ার মতো কিছু হবে না।
এদিকে ট্রাম্পের শুল্ক নীতি যেসব দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলেছে, সেগুলো আরও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হুয়াওয়ে ও জেডটিইয়ের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা চীনের প্রযুক্তি খাতে অগ্রগতির ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন নতুন করে ভূরাজনৈতিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলো চীনের শাসকদের জন্য জনগণকে ‘বিদেশিদের অপমান’-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ করে দিচ্ছে। শুল্কে সাময়িক বিরতি চীনা রপ্তানিকারকদের পণ্য পাঠানোর একটু সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু সেটি কোনো স্থায়ী শান্তিচুক্তি নয়।
এ শুল্ক ধাক্কা যখন এল, তখন চীন তাদের ১৪তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে ছিল। সে কারণে চীনা নীতিনির্ধারকেরা অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে এবং ছোট ব্যবসাগুলোকে বাঁচাতে সরকারি ব্যয় ও মুদ্রানীতির সাহায্য নিয়েছে। কিন্তু এগুলো চীনের অর্থনীতির গঠনগত সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে না। এ ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে আরও বহু বছর লাগবে।এখন বাইরের দুনিয়া চীনের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। এ সময়ে চীনের শীর্ষ নেতা ও বড় ব্যবসায়ীরা (যাঁদের অনেকেই প্রকৌশলে পড়েছেন) দেশের উন্নত প্রযুক্তি খাতে বেশি করে পয়সাকড়ি ঢালছেন। তাঁরা বিশেষভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে নতুন ধরনের আধুনিক কারখানা গড়তে মনোযোগী হয়েছেন।
২০১৮ সালে ট্রাম্প যখন চীনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করেন, তখন থেকেই চীন সিদ্ধান্ত নেয়, তারা নিজেদের প্রযুক্তি নিজে তৈরি করবে। এখনো সেই চেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্র যখন চীনকে চেপে ধরছে, তখন চীনের সামনে এ প্রযুক্তি উন্নয়নের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো সহজ পথ খোলা নেই।
জংইউয়ান জো লিউ কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের চীনবিষয়ক গবেষক
সত্ত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ