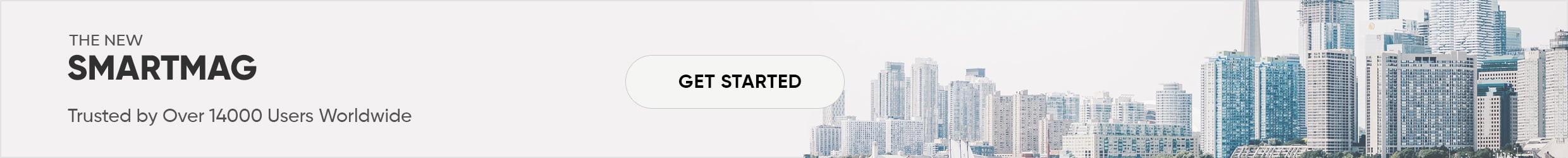ভাষা জন্মাল কীভাবে? এ এক প্রাচীন ধাঁধা। এই প্রশ্ন ভাবিয়েছে পুরোনো দিনের দার্শনিকদের, ভাবাচ্ছে আজকের ভাষাতাত্ত্বিকদেরও। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে অবশ্য বিবর্তনের তত্ত্ব বেশ গভীর ছাপ ফেলেছে।
প্রাচীনকালে কিন্তু অনেক রকম মত ছিল। এক দল মনে করত, ভাষার জন্ম স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা বা ইলহাম থেকে। এই পথের পথিক ছিলেন আবু আলী ফারসি ও ইবনে হাজম আন্দালুসির মতো পণ্ডিতেরা। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরতেন সুরা বাকারার ৩১ নম্বর আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে—‘তিনি আদমকে সব নাম (আসমা) শিক্ষা দিয়েছেন।’
তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, আল্লাহ স্বয়ং আদমকে আরবি, ফারসি, সিরীয় বা হিব্রুর মতো কিছু মৌলিক ভাষার মাধ্যমে সব প্রাণী আর জড়বস্তুর নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন।
তাওরাত অনুসরণ করে হিব্রু পণ্ডিতেরাও প্রায় একই কথা বলেন। এমনকি গ্রিক ও রোমান দার্শনিকদের মধ্যেও এই ধারণার ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। প্লেটোর মতে, ভাষা আসলে ঈশ্বরের দেওয়া এক উপহার। হেরাক্লিটাস বলতেন, ভাষা হলো স্বর্গীয় এক উন্মোচন। প্রাচীন ভারতেও বিশ্বাস করা হতো, মানুষকে ভাষা শিখিয়েছেন স্বয়ং ইন্দ্র, বৈদিক যুগের এক বিশিষ্ট দেবতা।
ভাষা মানুষেরই সৃষ্টি। আল্লাহ কেবল মানুষকে ভাষা শেখার ক্ষমতাটুকু দিয়েছেন, একেবারে হাতে ধরে সব শিখিয়ে দেননি। আদমকে ‘আসমা’ শেখানোর অর্থ এটাই।
কিন্তু দার্শনিকদের অন্য একটি দল এ কথা মানতে নারাজ। তাঁদের মতে, ভাষা মানুষেরই সৃষ্টি। আল্লাহ কেবল মানুষকে ভাষা শেখার ক্ষমতাটুকু দিয়েছেন, একেবারে হাতে ধরে সব শিখিয়ে দেননি। আদমকে ‘আসমা’ শেখানোর অর্থ এটাই। দার্শনিক ফারাবি বা ভাষাতাত্ত্বিক ইবনে জিন্নির মতো মানুষেরা এই মতেরই পক্ষে ছিলেন। (মানজিলাতুল লুগাতিল আরবিয়্যাহ, ড. আবদুল মাজিদ উমর)
আবার আরেকটা মতও চালু আছে। সেটা হলো, মানুষের অনুকরণ করার স্বভাব থেকেই ভাষার জন্ম। মানুষ হয়তো প্রকৃতির নানা পশুপাখি বা অন্য কিছুর আওয়াজ শুনেছে, তারপর সেটা নকল করার চেষ্টা করেছে। এভাবেই হয়তো সে প্রথম নিজের বাক্শক্তি টের পায়। (কিতাবুল খাসায়েস, ইবনে জিন্নি)
সেমেটিক পরিবারের সদস্য
আধুনিক ভাষাবিদেরা আরবিকে সেমেটিক ভাষা পরিবারের অংশ বলে মনে করেন। আঠারো শতকের শেষে জার্মান পণ্ডিত আগস্ট লুডভিগ ভন শ্লুজার প্রথম এই পরিবারের কথা বলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, আরামাইক, ফিনিশীয়, হিব্রু, আরবি, ইয়েমেনি, ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় ভাষার মধ্যে গভীর আত্মীয়তার টান আছে। শব্দ, গঠন বা বাক্যবিন্যাসের দিক থেকে এদের মধ্যে খুব মিল।
ইন্দো–আর্য ভাষাদের যেমন লাতিন, গ্রিক ও সংস্কৃতে ভাগ করা হয়, সেমেটিক পরিবারকেও তিনটি প্রধান শাখায় ভাগ করা হয়ে থাকে—আরামাইক, কেনানীয় ও আরবি। সিরীয়, ক্যালডিয়ান বা অ্যাসিরীয় ভাষার জন্ম ওই আরামাইক থেকে। আর কেনানীয় ভাষা থেকে এসেছে হিব্রু বা ফিনিশীয় ভাষা।
এই সেমেটিক বা সামি নামটা এল কোথা থেকে? আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ তাঁর আশতাতুম মুজতামিআত বইয়ে এর উত্তর দিয়েছেন। হিব্রু বাইবেল আর খ্রিষ্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্টে নুহ (আ.)–এর তিন ছেলের কথা আছে—সাম, হাম ও ইয়াফেস।
সাম এসেছিলেন আরব উপদ্বীপে। তাঁর নাম থেকেই ‘সামি’ বা ‘সেমেটিক’ শব্দটি এসেছে। হাম চলে যান আফ্রিকায়, আর ইয়াফেস ইউরোপে। এ ঘটনার উল্লেখ হাদিসেও পাওয়া যায়। তিরমিজির এক বর্ণনায় হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ‘সাম আরবদের পিতা, ইয়াফেস রোমানদের ও হাম হাবশিদের পূর্বপুরুষ।’ প্রচীন নিজামিয়া মাদরাসার দেয়ালে অংকিত একটি আরবি লিপি
প্রচীন নিজামিয়া মাদরাসার দেয়ালে অংকিত একটি আরবি লিপিছবি: উইকিপিডিয়া
ভাষার বাঁধন
সেমেটিক ভাষাগুলোর মধ্যে শব্দের মিল অবাক করার মতো। ড. হাজেম কামালুদ্দিন এই মিলগুলো নিয়ে মুজামু মুফরাদাতিল মুশতারাকিস সামি ফিল লুগাতিল আরবিয়্যাহ নামে একটি আস্ত অভিধান লিখেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন—
পানিকে আরবিতে বলে ‘মা’। এটাই ইথিওপিক ভাষায় ‘মাই’, আক্কাদীয় ভাষায় ‘মো’, উগারিতীয় ভাষায় ‘মি’, আরামাইকে ‘মিয়া’ ও হিব্রুতে ‘মাবাম’।
ঘরকে আরবিতে বলা হয় ‘বাইত’। এটাই ইথিওপিকে ‘বিত’, আক্কাদীয়তে ‘বেত’, উগারিতীয়তে ‘বাত’, আরামাইকে ‘বিতা’ ও হিব্রুতে ‘বাইতা’।
শান্তির জন্য আরবি শব্দ ‘সালাম’। ইথিওপিক ভাষায় সেটা ‘সিলাম’, আক্কাদীয়তে ‘শালাম’, উগারিতীয়তে ‘শাল্লাম’, আরামাইকে ‘শালামা’ ও হিব্রুতে ‘শালোম’।
শুধু শব্দই নয়, উচ্চারণেও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বদল ঘটেছে। ভাষাতাত্ত্বিক ড. রমজান আবদুত তাওয়াব তাঁর আল–লুগাতুল ইবরিয়্যাহ বইয়ে দেখিয়েছেন, হিব্রুতে যেটা ‘শ’, সেটাই আরামাইকে ‘ত’ আর আরবিতে ‘ছ’। যেমন ষাঁড় আরবিতে ‘ছাওর’, আরামাইকে ‘তাওরা’ ও হিব্রুতে ‘শাওরা’।
অনেক আগেই পণ্ডিতেরা এই সম্পর্কগুলো টের পেয়েছিলেন। যেমন আরবির প্রাচীন অভিধান ‘আল–আইন’–এর রচয়িতা খলিল বিন আহমাদ ফারাহেদী (মৃত্যু ১৭৫ হিজরি) বলেছিলেন, কেনানীয়দের ভাষা আরবির খুব কাছাকাছি।
আবার ইবনে হাজম আন্দালুসি জোর দিয়ে বলেছেন, সিরীয়, হিব্রু ও আরবি—এ তিনটি ভাষার উৎস একই, প্রাচীন মুদার গোত্র। পরে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ায় ভাষায় বদল এসেছে। আবু হাইয়ান তাওহিদিও আরবি ও ইথিওপিক ভাষার মধ্যে শব্দ, ব্যাকরণ ও লিঙ্গগত অনেক মিল খুঁজে পেয়েছিলেন।
হিব্রুতে যেটা ‘শ’, সেটাই আরামাইকে ‘ত’ আর আরবিতে ‘ছ’। যেমন ষাঁড় আরবিতে ‘ছাওর’, আরামাইকে ‘তাওরা’ ও হিব্রুতে ‘শাওরা’।
সেমেটিক ভাষাগুলোয় শব্দের জগৎটা দাঁড়িয়ে আছে তিন বা কালেভদ্রে চার অক্ষরের একেকটি ধাতুমূলের ওপর। একটি মাত্র মূল থেকেই জন্ম নেয় ডজন ডজন শব্দ, আর তাদের মধ্যে থাকে এক আশ্চর্য পারিবারিক টান।
ভাবা যাক, আরবির ‘ক–ত–ব’ ধাতুমূলটির কথা, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেখালেখির ধারণা। এই এক শিকড় থেকেই গজিয়েছে ‘কিতাব’ (বই), ‘মাকতাব’ (অফিস বা দপ্তর), ‘মাকতাবা’ (লাইব্রেরি), ‘কাতিব’ (লেখক), আবার ‘মাকতুব’ (যা লেখা হয়েছে অর্থাৎ চিঠি বা ভাগ্য)।
এর ফলে শব্দগুলোর মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র তৈরি হয়। একবার ধাতুমূলটা চিনে ফেললে বাকি শব্দগুলোর মানেও স্বচ্ছ হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।
তবে আরবির নিজস্ব কিছু ব্যাপারও ছিল। আবু উবাইদ কাসেম বিন সালাম বলেছিলেন, নির্দিষ্ট করে কিছু বোঝাতে আরবিতে শব্দের আগে ‘আলিফ–লাম’ বা ‘আল’ যোগ করা হয়, যা আশপাশের অন্য কোনো ভাষায় নেই।
আরবির উৎস সন্ধান
বিশুদ্ধ আরবির জন্ম আরব উপদ্বীপের উত্তরে প্রাচীন আদনানীয় জনগোষ্ঠীর মুখে। দক্ষিণের আরবির সঙ্গে এর উচ্চারণ ও শৈলীর বেশ অমিল ছিল। সেই দক্ষিণি ভাষা হিম্যারাইট নামে পরিচিত, আর তাতে কথা বলত কাহতান জনগোষ্ঠী। (আহমাদ হাসান জাইয়াত, তারিখুল আদাবিল আরবি)
কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। আচ্ছা, সবার প্রথম আরবিতে কথা বলেছিলেন কে? কেউ বলেন, ইয়ারব বিন কাহতান। তাঁর নাম থেকেই নাকি ‘আরবি’ শব্দটা এসেছে। আবার অনেকের মতে, প্রথম আরবি বলেছেন হজরত ইসমাইল (আ.)।
এ বিষয়ে ইবনে হাজার ফাতহুল বারি গ্রন্থে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেখানে হজরত মুহাম্মদ (সা.)–কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ইসমাইল (আ.) ১৪ বছর বয়সে প্রথম বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলেন। এর আগে মানুষ হিব্রু ভাষায় কথা বলত। মজার ব্যাপার হলো, বুখারি শরিফেরই অন্য একটি বর্ণনায় (হাদিস: ৩,৩৬৪) বলা হয়েছে যে ইসমাইল (আ.) মরুভূমিতে আসার পর সেখানকার স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে আরবি শেখেন। তাহলে এই দুই বর্ণনার মধ্যে কোনটি ঠিক?
ইবনে হাজার আসকালানি এর এক চমৎকার সমাধান দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইসমাইল (আ.) আরবি ভাষার প্রথম কথক নন; বরং তিনি ভাষাটির এমন এক বিশুদ্ধ রূপ দিয়েছিলেন, যা আগে কেউ পারেননি।
কাস্তাল্লানিও প্রায় একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ইব্রাহিম (আ.)–এর বংশে ইসমাইল (আ.)–ই প্রথম আরবিতে কথা বলেন, ব্যাপারটা আপেক্ষিক।
অবশ্য আরেকটি মতে, হজরত আদম (আ.)–ই প্রথম আরবিসহ পৃথিবীর সব ভাষায় কথা বলেছিলেন, কারণ আল্লাহ তাঁকে সবকিছুর নাম শিখিয়েছিলেন।
আরবির স্বাতন্ত্র্য
আরবি ভাষার এমন কিছু বিশেষত্ব আছে, যা তাকে সেমেটিক ভাষা পরিবারের অন্যদের থেকে এক আলাদা মর্যাদা দেয়।
১. সেমিটদের প্রাচীনতম বাসভূমি আরব উপদ্বীপেই আরবির জন্ম।
২. আরবি এমন এক ভৌগোলিক অবস্থানে বেড়ে উঠেছে, যেখানে বিদেশি ভাষার সঙ্গে তার মেলামেশা হয়েছে খুব কম। তাই সে তার সেমেটিক বৈশিষ্ট্যগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে ধরে রাখতে পেরেছে।
৩. অন্য সেমেটিক ভাষায় যতগুলো হরফ বা উচ্চারণ পাওয়া যায়, তার সব কটিই আরবিতে আছে। শুধু তা–ই নয়, আরবিতে ‘ছা’, ‘যাল’, ‘আইন’, ‘দোয়াদ’, ‘যোয়া’–এর মতো কিছু বাড়তি হরফও আছে।
৪. বিশেষ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে আরবি ভাষাবিদদের অনেক আদরযত্ন পেয়েছে। ফলে এর ব্যাকরণ ও শব্দভান্ডার অন্য সেমেটিক ভাষার চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ।
৫. ইসলামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরবির ব্যবহারকারীর সংখ্যাও কয়েক শতকের মধ্যে বহুগুণ বেড়ে যায়, যা অন্য কোনো সেমেটিক ভাষার ক্ষেত্রে হয়নি।
আজকের দিনেও যে আরবি শেখে, সে সহজেই ইমরুল কায়েসের কবিতার রসাস্বাদন করতে পারে। জাহেলি যুগের কোনো কবির কাছে আজকের দিনের কোনো আরবি বই পাঠালেও তিনি তা অনায়াসে বুঝতে পারতেন।
সাধারণত কোনো ভাষা অন্য ভাষার সঙ্গে না মিশলে ধীরে ধীরে মরে যায়। কিন্তু আরবির ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। সে অন্য ভাষা থেকে দূরে থেকে নিজের বিশুদ্ধতা ও মৌলিকত্বকে রক্ষা করেছে। বিশ্বায়নের এই যুগেও তার সেই কাঠামো নষ্ট হয়নি।
তাই আজকের দিনেও যে আরবি শেখে, সে সহজেই ইমরুল কায়েসের কবিতার রসাস্বাদন করতে পারে। জাহেলি যুগের কোনো কবির কাছে আজকের দিনের কোনো আরবি বই পাঠালেও তিনি তা অনায়াসে বুঝতে পারতেন। ভাষার এই অদ্ভুত স্থিতিশীলতা আরবির এক বড় শক্তি।
ড. আবদুস সবুর শাহিনের কথায় বিষয়টি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ‘সুদূর অতীত থেকে ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আরবি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তারা যেভাবে আরবি বলতেন, আমরাও সেভাবে বলি। অনারবীয় প্রভাব এতে বাধার সৃষ্টি করেনি। ধ্বনি, শব্দ, ধাতু ও বাক্যগঠন সেই আগের মতোই আছে। এই বৈশিষ্ট্য বিশ্বের অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে বিরল।’